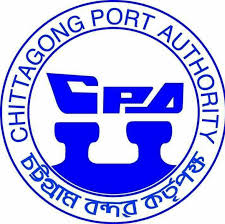চট্টগ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩:
১৯৪৮-এর মার্চ থেকে ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় চট্টগ্রাম।
পাকিস্তানের গণপরিষদের বাংলাবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম শহরেও ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘট,বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয়।
চট্টগ্রামে সে সময় সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ দলীয় রাজনীতি ও তাদের প্রভাবিত প্রশাসনের প্রবল প্রভাবের কারণে ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলন চট্টগ্রামে আশানুরূপ সাফল্য না না পাওয়ার মধ্যেই প্রগতিবাদী কর্মীরা এবং সাহিত্যকর্মীরা মুসলিম লীগ ও তাদের মদদপুষ্ট মাস্তানদের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন।
মাহবুব-উল আলম চৌধুরী, শহীদ সাবের, গোপাল বিশ্বাস প্রমুখ প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হয়।
স্বনামখ্যাত সাহিত্য গবেষক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাও পণ্ড হয়।
চট্টগ্রামে ১১ মার্চ থেকে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয় যা ১৪ মার্চ পর্যন্ত একটানা চলে।
আন্দোলনের ব্যাপকতা লক্ষ করে বিচলিত প্রশাসন ১৪ মার্চ এক সপ্তাহের জন্য ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা দেয়।
পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ১৯৪৮-এর মার্চে ঢাকা সফর ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দিয়ে চট্টগ্রামে আসলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা হয় চট্টগ্রামে।
১৯৫০ এ চট্টগ্রাম ভাষা আন্দোলনে আবার যুক্ত হয়।
কেন্দ্রীয় সরকারের মূলনীতি কমিটির উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে রাজনীতিক ও ছাত্ররা প্রতিবাদ করে।
রফিউদ্দিন সিদ্দিকীকে সভাপতি এবং রেলওয়ে শ্রমিকনেতা মাহবুবুল হক ও কবি, সম্পাদক মাহবুব-উল আলম চৌধুরীকে সম্পাদক মনোনীত করে একটি ভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।
কমিটি লালদীঘি ময়দানে জনসভা ও মিছিল আয়োজন করে।
এরমধ্যে বাংলা ভাষাবিরোধি গোষ্ঠী ফজলুল কাদের চৌধুরীর সহ উর্দু ও আরবি হরফে বাংলা লেখার পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালায়।
সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শ্রমিক ফ্রন্টের প্রগতিশীলরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে সামিল হয়।
শ্রমিকনেতা মাহবুবুল হক চৌধুরী, হারুনুর রশিদ, সাহিত্যকর্মী মাহবুব-উল আলম চৌধুরী, সুচরিত চৌধুরী, গোপাল বিশ্বাস, শহীদ সাবের, অধ্যাপক ফেরদৌস খান প্রমুখ স্থানীয়দের সঙ্গে চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক কথাশিল্পী শওকত ওসমানও যোগ দেন।
ছাত্ররা ১৯৪৯ সালে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীরা এবং প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের উদ্যোগে ১৯৫১-এর মার্চে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।সম্মেলনের সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন চৌধুরী হারুনুর রশিদ ও মাহবুব-উল আলম চৌধুরী।
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শওকত ওসমান ও সাইদুল হাসান। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল।
প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা থেকে আসা সত্যযুগসম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তার সাংস্কৃতিক দলে ছিলেন সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ সংগীতশিল্পী।
সিলেট থেকে আসেন নওবেলাল সম্পাদক মাহমুদ আলী এবং ঢাকা থেকে আলাউদ্দিন আল-আজাদ প্রমুখ তরুণ সাহিত্যকর্মীগণ।
অসাম্প্রদায়িক,গণতন্ত্রী, প্রগতিবাদী আবহ তৈরি এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সন্ত্রাসী দমননীতির বিরুদ্ধে এ সম্মেলন ছিল একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে জনমত তৈরির অনুকূল পদক্ষেপ।
এরপর ঢাকার অনুসরণে চট্টগ্রামেও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।
পরিষদের আহ্বায়ক তরুণ কবি মাহবুব- উল আলম চৌধুরী এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রমিকনেতা চৌধুরী হারুনুর রশিদ এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা এম এ আজিজ। কমিটিতে ছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী, ডা. আনোয়ার হোসেন, রুহুল আমীন নিজামী, গোপাল বিশ্বাস, সুনীল মহাজন প্রমুখ।
তাদের সাথে যোগ দেন ছাত্র-শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও যুবলীগের পাশাপাশি আওয়ামী মুসলিম লীগ, গণতন্ত্রী দল এবং নেপথ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি।
ছিলেন রিকশা শ্রমিক থেকে শ্রমিক ইউনিয়ন। তমদ্দুনন মজলিস এবং যুব ব্রিগেড নেতা কৃষ্ণগোপাল সেন। প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে ছিলেন কবিয়াল রমেশ শীল ও গণসংগীতশিল্পী মলয় ঘোষ দস্তিদার, সর্বহরি পাল, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, মাহবুব হাসান প্রমুখ।
১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রতিবাদী সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে ব্যাপক প্রচার ও দেয়ালে দেয়ালে পোস্টারে চট্টগ্রাম এক নতুন রূপ ধারণ করে।
২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) হরতাল, মিছিল, স্লোগান, সভা- সমাবেশে শহর চট্টগ্রাম সরগরম হয়ে ওঠে। ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’, ‘আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না’ ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে চট্টগ্রাম।
সাংস্কৃতিক কর্মীদের নেতৃত্ব দেন আবুল ফজল। মেডিকেল স্কুল থেকে কারিগরি প্রতিষ্ঠানও একুশের ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়।
মিছিলে মিছিলে ভরে উঠে লালদীঘি মাঠ
লালদীঘির জনসভার পর শহরের প্রধান সড়কগুলোতে প্রায় ৪০ হাজার জনতার মিছিল স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে।
ঢাকায় গুলিবর্ষণের খবর শুনে মাহবুব-উল আলম চৌধুরী লেখেন দীর্ঘ কবিতা, “কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি”।
পরবর্তী দিনগুলো আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠে। ছাত্রীরাও যোগ দেন। মার্চেও আন্দোলনে উত্তাল ছিল চট্টগ্রাম।
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রামে। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীরাই আন্দোলনের অগ্রভাগে।
হাটহাজারী, বোয়ালখালী, ফটিকছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান এমনকি সাগরদ্বীপ সন্দ্বীপে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।
চট্টগ্রামেরই গণপরিষদ সদস্য নূর আহমদ পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করেন।
কিন্তু তার দল মুসলিম লীগের চাপে তাকে পিছিয়ে আসতে হয়।
সূত্র: প্রখ্যাত লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ আহমদ রফিকের ‘ভাষা আন্দোলন- টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া গ্রন্থ থেকে’ লিখেছেন প্রান্তিক দাশ।