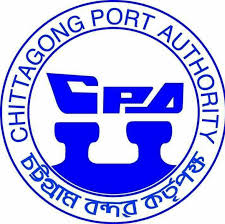চট্টগ্রাম, ১ ডিসেম্বর, ২০২৩:
যুদ্ধ শুরুর আগে পুরোটা সময় ধরে চারপাশ জুড়ে সকলের মুখে মুখে সম্ভাব্য চীনা আক্রমণ নিয়ে কথাবার্তা শোনা গেছে। তিব্বতে অবশ্য কোনো ধরনের চীনা সেনাসমাবেশ দেখা যায়নি। ইস্টার্ন কম্যান্ডের ধারণা, চীনাদের ফরমেশন ও বিন্যাস তাৎক্ষণিক আক্রমণ রচনার উপযোগী নয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে হিমালয়ের অধিকাংশ গিরিপথই ব্যবহার করা অসম্ভব। অবশ্য সেনাপ্রধানের সোভিয়েত-পরামর্শপুষ্ট ধারণা ছিল এরকম যে, যুদ্ধ শুরু হলেই চীনারা হস্তক্ষেপ করবে। আর এসব সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি জেনারেল মানেকশ’র ওপরে অন্যায় রকমের প্রভাব ফেলত। এই বিভ্রান্তির মধ্যে মার্কিনীরাও নতুন মাত্রা যোগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা (L K Jha)-কে ডেকে নিয়ে হেনরি কিসিঞ্জার (Henry Kissinger) হুঁশিয়ার করে দেন যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করলে ওয়াশিংটন ভারতকে সাহায্য করবে না। ভারত সরকারের কাছে পাঠানো জরুরি এক টেলিগ্রামে ঝা জানান যে, কিসিঞ্জার যেহেতু ‘জানেন না চীনারা কী করবে, তারা পাকিস্তানের পক্ষে যে আসবে না – এমন ধারণা নিয়ে বসে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ নয় (…did not know what the Chinese would do, it would be unsafe for us to assume that they would not come to Pakistan’s help)’। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, অথচ ঢাকা আক্রমণের জন্য তখন পর্যন্ত সৈন্যের সংস্থান করা হয়ে ওঠেনি। বিষয়টি নিয়ে – বিশেষত ১৬৭ ও ৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের জন্য যে – কর্ম-পরিকল্পনা আমরা নির্ধারণ করে রেখেছিলাম, তা নিয়ে আমি ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্সের সাথে আলোচনা করি। ১২৩ মাউন্টেন ব্রিগেডও রিজার্ভ হিসেবে চলে এসেছে। নভেম্বরের শেষের দিকে আর্মি কম্যান্ডারের কাছে এসব ব্রিগেডের গতিপথ ও তাদের কর্ম-পরিকল্পনা আমি ব্যাখ্যা করি। তিনি আমাকে এসব বিধি মোতাবেক আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে জানাতে বলেন। আমি তাঁকে জানাই যে, ইন্দর গিল এসব জানেন, কিন্তু জেনারেল মানেকশ’কে তিনি কিছু জানাননি। লড়াই শুরু হলে চীনারা হস্তক্ষেপ করবেই, মানেকশ’ এরকম ধারণা নিয়ে থাকায় তিনি কিছুতেই চীন- সীমান্ত থেকে সৈন্য সরাতে রাজি হবেন না। এরপরে তিনি বললেন যে, তিনি নিজেই মানেকশ’কে একটি বার্তা পাঠাবেন। এই কাজটি না করার জন্য আমি আবার তাঁকে অনুরোধ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি মানেকশ’কে একটি ব্যক্তিগত সিগন্যাল পাঠান। দুই ঘণ্টার মধ্যে এর উত্তর এল: যে কোনো নারীর চেয়ে বেশি যত্নে আমি আপনাদেরকে লালনপালন করেছি। কে আপনাদেরকে এই ব্রিগেডগুলো সরাতে বলেছে? শিগগির এগুলোকে আগের জায়গায় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন (I have nursed you better than any woman. Who told you to move these brigades down? You will move them back at once.) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার সেথনা ও লেফ্টন্যান্ট কর্নেল দাল সিং (Dal Singh) এই জবাব নিয়ে আমার অফিসে এলেন। আমি সেটা আর্মি কম্যান্ডারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আর্মি কম্যান্ডার যখন আমার অফিসে ঢুকলেন, তাঁকে তখন কিছুটা বিধ্বস্ত দেখা যাচ্ছিল। আমি তাঁকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে বললাম, “বিষয়টি নিয়ে আমি ডিএমও ইন্দর গিলের সাথে কথা বলব।” ইন্দরকে আমি ফোন করে বললাম, “ব্রিগেড এই মুহূর্তে সরানো অসম্ভব, কারণ অপারেশনের জন্য তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে।” অন্যদিকে আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে, চীনারা যে এতে হস্তক্ষেপ করবে না, এই বিষয়টি আমরা ধীরে ধীরে মানেকশ’কে বোঝাতে সক্ষম হব। ইন্দর গিল রাজি হলেন, কিন্তু আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে আমি সৈন্যদেরকে পাঠাব না। পরবর্তীতে ডিসেম্বরের ৮ তারিখে বারংবার অনুরোধে মানেকশ’ যখন বুঝলেন যে, চীনারা এতে হস্তক্ষেপ করবে না, তখন তিনি আমাদেরকে ১৬৭ ও ৫ মাউন্টেন ব্রিগেড ব্যবহারের অনুমতি দেন। এর আগে ইন্দরের অনুরোধে ডিসেম্বরের ৬ তারিখে ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডকে আরো সুসংহত করার লক্ষ্যে ১২৩ মাউন্টেন ব্রিগেডকে বিমানযোগে সেখানে পাঠানো হয়। আমাদের বাহিনী সেখানকার অপারেশনে তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, যথাযথভাবে দায়িত্বপালন এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা যে ইন্দরের আছে, তা তিনি আরেকবার প্রমাণ করলেন। এর মধ্যে বিশ্ব-জনমত ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আসতে শুরু করেছে। বিদেশী সাংবাদিকরা শরণার্থী শিবির ঘুরে দেখেছেন এবং বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে ঘুরে এসেছেন। পাকিস্তানিদের নৃশংসতা দেখে তাঁরা বেদনায় আপ্লুত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের পক্ষে নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। প্রায় সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র ও চীন অবশ্য পাকিস্তানকে সমর্থন করে। জাতিসংঘের অবস্থানও ছিল পাকিস্তানঘেঁষা। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের সময় হিমালয় সীমান্ত অঞ্চলে চীন আমাদেরকে স্রেফ ভয় দেখাবার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে চীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবারেও আমরা বুঝতে পারছি না। ৬ জুলাই ইসলামাবাদ যাবার পথে ড. হেনরি কিসিঞ্জার দিল্লীতে অবতরণ করেন। ইয়াহিয়া খান ড. কিসিঞ্জারের চীন সফরের ব্যবস্থা করেন। কিসিঞ্জার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরের ব্যবস্থা করেন। পাকিস্তানের প্রতি মার্কিনী সমর্থন বাড়াতে এবং জাতিসংঘে চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে পাকিস্তানি কূটনৈতিক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক স্থাপনের জন্য ইউ থান্ট (U Thant) একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের এই প্রস্তাবনা আমাদের জন্য বেশ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ওপরে পশ্চিম পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানের পক্ষে চীন ও আমেরিকার সমর্থন বাড়ার সাথে সাথে পাকিস্তানের সাথে আমাদের সম্ভাব্য যুদ্ধে চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কাও বেড়ে যায়। এই সঙ্কটের পুরোটা সময় জুড়ে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার স্বাক্ষর-রাখা শ্রীমতি গান্ধীর উদ্যোগে ডি পি ধরের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী চুক্তি প্রণয়নের ব্যাপারে মস্কোর মনোভাব জানার লক্ষ্যে কিছু বার্তা পাঠানো হয়। ডি পি ধর ১৯৬৯ সালে যখন মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, সেই তখন থেকেই তিনি এই চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। সোভিয়েত-পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়, এবং তা খুবই দ্রুত। মৈত্রী চুক্তির এমন একটি খসড়া তৈরি করা হয়, যা ভারতের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উপযুক্ত এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব বা জোটনিরপেক্ষ নীতি অক্ষুণ্ণ রেখেই এর বাস্তবায়ন সম্ভব। এটি অবশ্যই একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য। ধারা ৯-এর মধ্যে এই চুক্তির মূল সুর নিহিত আছে, যেখানে বলা হয়েছে, “যে কোনো পক্ষ অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হলে বা তেমন কোনো হুমকির সম্মুখীন হলে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহ এ ধরনের হুমকির কারণ অপসারণ করে শান্তি ও তাদের রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে পরস্পরের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।” এটা ভারতকে নিঃসন্দেহে চীন ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক হাবভাব ও হুমকির উপযুক্ত জবাব দেবার ব্যাপারে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে (পরিশিষ্ট ১৭ দ্রষ্টব্য)। ইতোমধ্যে দিল্লীস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কলকাতার মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব এ কে রায় (A K Ray)-কে এই দায়িত্ব দিয়ে কলকাতায় পাঠানো হয়। দক্ষ অফিসার রায় সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ ও পরিস্থিতির সাথে ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। কথাবার্তা ও আচরণে তিনি ছিলেন খুবই বাস্তববাদী এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশী নেতৃত্বের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হন। ডি পি ধর ছিলেন পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান। পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে রীতিমতো উপেক্ষা করে ডি পি ধর, পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউল (T N Kaul), পি এন হাকসার (P N Haksar) ও পি এন ধর (P N Dhar)- এর সমন্বয়ে গঠিত অত্যন্ত দক্ষ ও প্রভাবশালী সোভিয়েতঘেঁষা এই গ্রুপটি যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। শক্তিশালী এই দলটিকে ‘কাশ্মিরী মাফিয়া’ নামে অভিহিত করা হয়। মুজিবনগরের সোভিয়েতঘেঁষা অংশটির ব্যাপারে ডি পি কিঞ্চিৎ দুর্বল ছিলেন। অগাস্টের শেষভাগ থেকে শুরু করে ডি পি ধর যখনই কলকাতায় এসেছেন, গ্র্যান্ড হোটেলের স্বত্বাধিকারীর স্যুইটে থেকে কাজকর্ম করেছেন। এর আগে কাশ্মিরেই ডি পি ধরের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং আলোচনার জন্য বেশ কয়েকবার তাঁর স্যুইটে তিনি আমাকে ডেকেছেন। আমাদের আলোচনা চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং অন্য অনেক ছোটখাট বিষয়ও আলোচনার মধ্যে ঢুকে যেত। কমিউনিস্টদের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ অদ্ভুত ধরনের। তাঁর মতে সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্টরা ‘ভাল লোক’ হলেও পূর্ব পাকিস্তানের মার্কসবাদীরা তেমন নয়। এই গ্রুপকে যে রাজনৈতিক বা সামরিকভাবে কোনো ধরনের সহায়তা করা উচিত নয়, সেটা আমি বারবার আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল, “জেক, আমি জানি আমি কী করছি।” সবসময় তিনি এ কে রায়কে এড়িয়ে চলতেন, যেটা নিঃসন্দেহে এক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। সারেন্ডারের অল্প কয়েকদিন পরে কলকাতা এয়ারপোর্টের ভিআইপি লাউঞ্জে ধরের সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাঁকে পরামর্শ দিই যে, এই সময়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন, যাতে তিনটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে: সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রসীমানার যৌক্তিকতা নির্ধারণ, এবং চট্টগ্রাম বন্দরসহ রেল ও অভ্যন্তরীণ জলপথে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ট্রানজিট ব্যবহারের অধিকার। ডি পি তাঁর ভুবনভোলানো হাসি নিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, “জেক, আপনি সৈনিক। আর এই সমস্যাগুলো রাজনৈতিক। পরে যথাসময়ে এসবের সমাধান করা যাবে।” আমি উত্তর দিলাম যে, এটাই উপযুক্ত সময় এবং এর পরে এ বিষয়ে কোনো চুক্তিতে পৌছানো কঠিন হয়ে যাবে। তিনি আবার হাসলেন। এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কোনো কথা বলেননি। সেপ্টেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনীর অপারেশনগুলো আগের তুলনায় অনেক সংগঠিত ও কার্যকর হতে শুরু করে এবং ক্রমশ তীব্রতা লাভ করে। তাদের কার্যকলাপ ঢাকাস্থ পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনীর সেইসব লোকদের মনোবল একেবারে ভেঙে দিতে শুরু করে, ইতোমধ্যেই যাদের মোহমুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। জাতিসংঘ ও চীনের সাথে পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতা তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলপ্রসূ হয়নি। ভারত তাদেরকে আক্রমণ করলে চীনের তরফ থেকে ভারত আক্রমণের কোনো নিশ্চয়তা লাভ করতে তারা ব্যর্থ হয়। চীনের ভূমিকা ছিল দ্বিমুখী। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সহজাত প্রজ্ঞা দিয়ে চীনারা বাংলাদেশের আসন্ন স্বাধীনতার বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং তারা এই নতুন দেশের সাথে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়নি। মার্কিন ভূমিকা ছিল আরো জটিল। ড. কিসিঞ্জার দাবি করেন যে, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন যে অবধারিত, এটা তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভারতকে জানিয়েছেন, যদিও দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিং (Keating) ৬ জানুয়ারি ১৯৭২-এ নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনকে যে সাক্ষাৎকার দেন, তাতে এধরনের কোনোকিছুর ব্যাপারে তাঁর অবগতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আমি ওয়াশিংটনস্থ তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝাকেও এই প্রশ্ন করলে তিনিও এব্যাপারে তাঁর অজ্ঞতা ব্যক্ত করেন (পরিশিষ্ট ১৯ দ্রষ্টব্য)। রাষ্ট্রদূত কিটিং এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম পরিদর্শন করেন। আর্মি কম্যান্ডার ট্যুরে থাকায় আমি তাঁকে বর্তমান পরিস্থিতি – বিশেষত শরণার্থী সমস্যা ও পাকিস্তানিদের ব্যাপক নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করি। তাঁকে আমি বলি যে, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশের সরকার কেন একটি নিষ্ঠুর উৎপীড়নকারী সামরিকতন্ত্রকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, যারা পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফলকে সম্পূর্ণ অসম্মান করেছে। কূটনীতিক হিসেবে কিটিং ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত। তাঁর সংবেদনশীল মুখ একটু লাল হয়ে উঠলেও তিনি আমার কথায় বিরক্তি প্রকাশ করলেন না বা তাঁর সরকারের অবস্থানের পক্ষেও কোনো কথা বললেন না। সম্ভবত স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা ড. কিসিঞ্জারের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিক্সনের পাকিস্তানপ্রীতির বিরোধিতা করার মতো ঘনিষ্ঠ ছিল না।
#লেখক- লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব ভারতের সেনা কর্মকর্তা। বাংলাদেশের মুক্তিযদ্ধের ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তার পুরো নাম-জ্যাকব ফ্রেডারিক রালফ জ্যাকব। লেখাটি এই সেনা কর্মকর্তার সারেন্ডার এট ঢাকা’ বইয়ের ‘মার্কিন ও চীন ভূমিকা’ অধ্যায়ের নাম পরিবর্তন করে পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হয়েছে।
লে. জেনারেল জে এফ আর জেকবের জন্ম ১৯২৩ সালে। মৃত্যু ২০১৬ সালের ১৩ জানুয়ারি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৭১ সালে সংগঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তার অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদ হতে অবসরগ্রহণকারী জেনারেল জ্যাকব ১৯৭১ সালে মেজর জেনারেল হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করেন। ৩৬ বছরের সেনাবাহিনী জীবনে তিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।