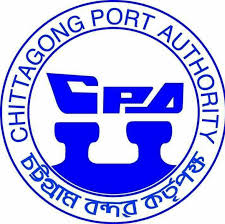#প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের লেখা গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন গ্রন্থ থেকে নেওয়া#
চট্টগ্রাম, ২২ নভেম্বর, ২০২৪:
বাংলাদেশের বাণিজ্যপ্রধান ও সবচেয়ে বড় বন্দর-শহর চট্টগ্রামে ৩০ লক্ষ লোকের বাস। শহরের পুরানো বাণিজ্যিক এলাকায় বক্সিরহাট রোডে আমি বড় হয়েছি। রাস্তাটি খুবই জনবহুল ও স্বল্প পরিসর। শুধুমাত্র একটি ট্রাক যেতে পারার মতো চওড়া, বক্সিরহাট রোড চাক্তাই নদী-ঘাট থেকে পণ্যাদি শহরের বাজারে যাবার প্রধান রাস্তা।
এই রাস্তার এক ধারে সোনাপট্টি। মণিকারদের অঞ্চল। আমরা এখানে ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ির উপরতলায় থাকতাম, বাড়ির নম্বর ছিল ২০ (এখন অবশ্য তা বদলে গেছে)। একতলার সামনের অংশে আমার আব্বার গহনার দোকান ও পিছনের অংশে কারিগরদের জায়গা ছিল। আমাদের জগৎ ছিল পেট্রোলের ধোঁয়া, ফেরিওয়ালা, জাদুকর, ভিক্ষুক, রাস্তার পাগলদের হাঁকডাক, নানান গোলমালে ভরা। রাস্তা আটকে সবসময় ট্রাক বা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। সারাদিন ধরে আমরা ট্রাক-ড্রাইভারদের চিৎকার, তর্কাতর্কি ও জোরদার হর্ন শুনতাম। যেন সবসময় উৎসব চলছে। অথচ এখানেই মাঝরাতের দিকে চারিদিক প্রায় নিঃশব্দ হয়ে আসত। আব্বার কারখানায় স্বর্ণকারদের হালকা হাতুড়ি পেটার ও পালিশ করার মৃদু আওয়াজ শোনা যেত। সর্বদা কিছু না কিছু শব্দ ছিল আমাদের জীবনের নেপথ্য ছন্দ। উপরতলায় শুধু চারটি ঘর ও একটি রান্নাঘর। আমরা ছোটরা নাম দিয়েছিলাম-‘মায়ের ঘর’, ‘রেডিয়ো ঘর’, ‘বড় ঘর’। চতুর্থটির কোনও নাম ছিল না। এখানে মাদুর বিছিয়ে তিনবেলা খাওয়া হত, যেখানে আমার আব্বার ছিল কর্তার আসন। বড়ঘরটি ছিল বাচ্চাদের থাকার ঘর। সবার একসঙ্গে এখানে শোওয়া হত।
তিনতলার রেলিং ঘেরা ছাদ ছিল আমাদের খেলার জায়গা। যখন একঘেয়ে লাগত আমরা নীচের তলায় আব্বার দোকানের খরিদ্দার, পিছনের ঘরে কর্মরত স্বর্ণকারদের কাজ দেখতাম। অথবা রাস্তার সারাক্ষণ বদলাতে থাকা এবং প্রায় একই ধরনের বিভিন্ন দৃশ্য দেখে সময় কাটাতাম।
চট্টগ্রামে ২০ নং বক্সিরহাট রোডে আসার আগে আব্বা অন্যত্র দোকান করতেন। সেটি ১৯৪৩ সালে জাপানি বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরিত্যক্ত হয়। জাপানিরা প্রতিবেশী দেশ বার্মাকে আক্রমণ করেছিল এবং চট্টগ্রামের প্রায় দুয়ারে এসে পড়েছিল। ব্রিটিশ ভারতও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আমাদের মাথার উপর আকাশ-যুদ্ধ কখনওই তেমন মারাত্মক হয়নি। জাপানি বিমান থেকে কাগজের ইস্তাহার ফেলা হত ও ছাদ থেকে তাই দেখতে আমরা ছোটরা ভারী মজা পেতাম। কিন্তু একবার বিমান হামলায় আমাদের বাড়ির দেওয়াল ধসে পড়ল। আব তাড়াতাড়ি পুরো পরিবারকে আমাদের আদিবাড়ি বাথুয়া গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। এই গ্রামেই আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জন্মেছিলাম।
শহর থেকে বাথুয়ার দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। আমার দাদা (আব্বার আব্বা) ছিলেন ছোট ব্যবসায়ী। তাঁর জমি ও খামার ছিল। কিন্তু তিনি পেশা বদলে স্বর্ণকারের ব্যবসা গ্রহণ করেছিলেন।
তাঁর বড় ছেলে আমার আব্বা দুলা মিয়া, হাইস্কুল শেষ করার আগেই পড়া ছেড়ে তাঁর আব্বার ছোট্ট ব্যবসায় লেগে গিয়েছিলেন। স্যাকরার কাজে প্রথাগতভাবে হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু অতি শীঘ্রই তিনি স্থানীয় মণিকার হিসেবে মুসলিম খরিদ্দারদের কাছে সুনাম অর্জন করেন।
আমার আব্বা ছিলেন কোমল স্বভাবের মানুষ। তিনি কদাচিৎ আমাদের শাস্তি দিতেন। কিন্তু আমাদের পড়াশুনোর ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন।
আজও কান পাতলে আমি আব্বার দোকানের সিন্দুকের ড্রয়ার টানার শব্দ শুনতে পাই। তাঁর চার ফুট উঁচু তিনটি লোহার আলমারি ছিল কাউন্টারের পিছনের দেওয়াল জুড়ে। যখন দোকান চালু থাকত তখন আলমারিগুলি খোলা থাকত। আলমারির পাল্লার ভিতরের দিকে আয়না এবং সাজানোর তাক করা ছিল। খরিদ্দারদের সেগুলি আলমারি বলে মনে হত না। মনে হত দোকানের সুন্দর শোকেস।
আমরা পড়ছি কি না তা দেখবার জন্য আব্বা উপরে উঠে আসতেন। তাঁর পায়ের শব্দ আমাদের খুব চেনা ছিল। রাতে এশার নামাজ পড়ার আগে বাবা আলমারির ড্রয়ার ঠেলে বন্ধ করতেন। আলমারি বন্ধ করবার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ আমরা শুনতে পেতাম। প্রতি পাল্লায় তিনটে তালা অর্থাৎ প্রত্যেক আলমারির ছটা করে তালা ছিল। এর ফলে আমি ও আমার বড় ভাই আবদুস সালাম তড়িঘড়ি অন্য কাজ ফেলে বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার যথেষ্ট সময় পেতাম। অবশ্য আব্বা যে পাঠ্যপুস্তকের কথা ভাবতেন, বইগুলি মোটেই তা নয়। কিন্তু তিনি কখনও ঠিক কী বই পড়ছি দেখবার জন্য পিছন থেকে উঁকি মারতেন না।
যখন তিনি দেখতেন সামনে বই খোলা ও আমাদের ঠোঁট নড়ছে, তিনি সন্তুষ্ট হতেন। “লক্ষ্মী ছেলে, ভাল ছেলে” বলে তিনি নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে রওয়ানা হতেন।
আমার আব্বা ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনবার তিনি হজ করতে মক্কায় গিয়েছিলেন। ভারী ফ্রেমের চশমায়, দুধ সাদা দাড়িতে তাঁকে দেখাত বিদগ্ধ মানুষের মতো। তিনি কোনওদিন বইয়ের পোকা ছিলেন না। বড় পরিবার ও সফল ব্যবসা সামলাতে গিয়ে আমাদের পড়াশুনোর দিকে খুঁটিনাটি লক্ষ রাখার সময় তার ছিল না। তিনি সবসময় সাদা পোশাক পরতেন-চটি, পাজামা, লুঙ্গি, গেঞ্জি, নামাজ পরার টুপি সবই সাদা। তাঁর সময় কেটে যেত দোকান, নামাজ ও সাংসারিক কর্তব্য সাধনের মধ্যে। কিন্তু আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনমনীয়।
আমার মা সুফিয়া খাতুন ছিলেন ব্যক্তিত্বময়ী ও দৃঢ়চেতা মহিলা। গোটা পরিবারের শৃঙ্খলারক্ষার ভার ছিল তাঁরই উপর। তিনি যদি তাঁর নীচের ঠোঁটটা কামড়ে কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন, আমরা জানতাম তার নড়চড় হবে না। তিনি চাইতেন আমরা তাঁর মতো সুশৃঙ্খল হয়ে উঠি। মা ছিলেন মমতার প্রতিমূর্তি। সম্ভবত তিনিই আমার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দূর গ্রাম থেকে দূর সম্পর্কের গরিব আত্মীয়রা দেখা করতে আসতেন। তাঁদের জন্য মার ভাঁড়ারে আলাদা করে টাকা রাখা থাকত। গরিব ও হতভাগ্যদের জন্য তাঁর সস্নেহ নজর সম্ভবত আমার ভবিষ্যৎ গন্তব্যস্থল আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল। তিনিই আমার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছিলেন।
তিনিও এক ছোট ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে, যাঁরা বার্মায় কারবার করতেন। তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার নানা (আম্মার আব্বা) জমিদারি মেজাজে থাকতেন। চাষের জমি ইজারা দিয়ে, বই পড়ে, দিনপঞ্জি লিখে তাঁর সময় কাটত। তিনি ভোজন রসিক ছিলেন। রকমারি খাওয়া-দাওয়া নিয়ে মেতে থাকতেন যার জন্য তিনি নাতিদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।
আমার ছোটবেলায় মাকে যেভাবে দেখেছি, আমার মনে পড়ে। পরনে রঙিন জরি পাড় শাড়ি, ডান দিকে সিঁথি করা ঘন কালো চুলে মস্ত খোঁপা বাঁধা। আমি তাঁকে অসম্ভব ভালবাসতাম। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি তাঁর আঁচল ধরে টানতাম।
খরা, বন্যা, ঝড় যাই হোক না কেন, চেষ্টা করলেও তিনি কখনও অসুন্দর হতে পারতেন না। পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময়ের উৎস ছিল তাঁর গলার গান ও গল্প। আবেগে ধরা গলায় তাঁর বর্ণিত কারবালা যুদ্ধের দুঃখের কাহিনী আমি আজও মনে করতে পারি। প্রতি বছর মহরমের সময় যখন আমরা সেই করুণ ঘটনার স্মৃতিচারণ করতাম তখন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতাম-
“মা, বাড়ির দিকের আকাশটা লাল ও অন্যদিকেরটা নীল কেন?”
হায়, নীল হল হাসানের জন্য ও লাল হল হোসেনের জন্য।” ”
“কারা এই হাসান, হোসেন?”
“তাঁরা দুজন আমাদের মহান পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের (দ.) নাতি। তাঁর পবিত্র দুই চোখের মণি।”
তিনি যখন তাদের মহাপ্রয়াণের কাহিনী শেষ করতেন তখন গোধূলির আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলতেন বাড়ির এদিকের আকাশের নীল রং হল বিষ যা হাসানের প্রাণনাশ করেছিল। অন্যদিকের লাল হল হোসেনের রক্ত। শিশুকালে তাঁর সেই বর্ণনা আমাকে এত মুগ্ধ করেছিল যে পরে বিখ্যাত বাংলা বিষাদ-সিন্ধু পাঠও আমার সেই মুগ্ধতাবোধকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি।
আমার ছোটবেলা মায়ের শাসনে কেটেছে। মা যখন রান্নাঘরে সুস্বাদু পিঠে বা মচমচে ভাজা কোনও নাস্তা বানাতেন তখন আমরা তাঁকে ঘিরে থাকতাম, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতাম, একটু চেখে দেখার জন্য দরবার করতাম। তাওয়া থেকে প্রথম পিঠেটি নামিয়ে ঠান্ডা করার জন্য মা যেই ফুঁ দিতে শুরু করতেন, আমি তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতাম। কারণ পরিবারের মধ্যে ভাল ‘চাখিয়ে’ বলে আমার বিশেষ মর্যাদা ছিল।
মার আরও অনেক কিছু আমায় মুগ্ধ করত। আমাদের দোকানে তৈরি অলংকারগুলির উপর তিনি কারুকাজ করতেন। গলার হার বা কানের দুলের সূক্ষ্ম কাজগুলি তিনি সযত্নে পরিপাটি করে শেষ করতেন। কোথাও একটু ভেলভেট, কোথাও এক গুচ্ছ পশমের ফিতে, কখনও বা বিনুনি করা মালা গাঁথার দড়ি বানিয়ে জুড়ে দিতেন। অভিভূত হয়ে আমি দেখতাম
তাঁর দীর্ঘ সরু আঙুলগুলি কেমন করে গয়নার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলছে। এ কাজে যে টাকা তিনি আয় করতেন তা বিলিয়ে দিতেন সাহায্যপ্রার্থী, অভাবী গরিব আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে।
চৌদ্দটি সন্তান জন্মেছিল তাঁর। এদের মধ্যে পাঁচটি সন্তান শিশুকালেই মারা যায়। এত বড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করে খুবই অল্পবয়সে আমি অনেক ভার নিতে শিখেছিলাম। শিশুপালন ও পারিবারিক বিশ্বস্ততার গুরুত্ব, পারস্পরিক নির্ভরতা ও সমঝোতার মূল্য বুঝতে শিখেছিলাম।
আমার আট বছরের বড় বোন (বুবু) মমতাজের বিয়ে হয়েছিল খুবই অল্পবয়সে। শহরের এক প্রান্তে তার শ্বশুরবাড়ি, আমাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। প্রায়ই আমরা সেখানে যেতাম। রকমারি রান্না খেয়ে আসতাম। বুবু মায়ের কাছ থেকে তিনটি গুণ পেয়েছিল। চমৎকার রান্নার হাত, প্রিয় মানুষজনকে তৃপ্তি করে খাওয়ানো এবং অসাধারণ গল্প বলার ক্ষমতা। সে গল্প কোনওদিন ফুরোবার নয়।
আমার তিন বছরের বড় ভাই সালাম আমার সারাক্ষণের সঙ্গী ছিল। জাপানি যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আমাদের মারামারি চলতেই থাকল। মুখে মেশিনগানের আওয়াজ করতে করতে জাপানি বিমান মনে করে আকাশে আমরা নানা রঙের ঘুড়ি উড়াতাম। দুখানি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি চৌখুপ্পি (diamond shaped) ঘুড়ি ছিল জাপানি বিমানের বিকল্প। আমাদের উত্তেজনা চরমে উঠল যখন আব্বা এরই মধ্যে ক’টা জাপানি বোমার খোল কিনে আনলেন। আম্মা সেগুলো ছাদে গাছের টবের কাজে লাগালেন।
আমি বাসার কাছেই লামারবাজার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। আমাদের এলাকার অধিকাংশ খেটে খাওয়া পরিবারের ছেলেরা ছিল আমার স্কুলের সহপাঠী। ছাত্র ও শিক্ষকেরা সেখানে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন। স্কুলের আর্থিক সংগতি থাকলে তবেই শিশুদের বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ থাকে। তবে এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিশেষ চেষ্টা ছিল খেটে খাওয়া পরিবারের বাচ্চাদের স্কুলে আনতে।
মেধাবী ছাত্ররা বৃত্তি পাবে এবং জাতীয় স্তরে পরীক্ষা দেবে-এটাই ছিল স্কুলের পক্ষে গৌরবের। অথচ দেখলাম আমার অধিকাংশ সহপাঠী শীঘ্রই স্কুল ছেড়ে দিল।
আমাদের সময়কার শিক্ষালয়গুলি ছাত্রদের মধ্যে সঠিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলত। বৃত্তি পাবার শিক্ষাগত জ্ঞানার্জন ছাড়াও এই শিক্ষা সমাজ সচেতনতা, আধ্যাত্মিক চেতনা, শিল্পানুরাগ, সাহিত্য ও সংগীতপ্রীতি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মতো কবিদের প্রতিভার উৎকর্ষ উপলব্ধি, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ ঘটাত।
বড়দা ও আমি হাতের কাছে বই বা পত্রিকা যা পেতাম সব পড়ে ফেলতাম। আমি রহস্য রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত ছিলাম। বারো বছর বয়সে আমি নিজেই গোটা এক রহস্যকাহিনী লিখে ফেলেছিলাম।
অবিরত পড়ার খোরাক জোগাড় করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। প্রয়োজন মেটাতে নিজেদেরই উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছিল-বই কেনা, ধার করা, এমনকি চুরি পর্যন্ত। আমাদের প্রিয় শিশুপাঠ্য পত্রিকা শুকতারা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। তাতে নিয়মিত একটি প্রতিযোগিতা থাকত, জিতলে বিনামূল্যে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যেত। পত্রিকায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের নাম ছাপা হত। তাদের মধ্যে একজনের নাম বেছে
আমি সম্পাদককে চিঠি লিখেছিলাম:
মাননীয় সম্পাদক,
আমি অমুক, একজন বিজয়ী প্রতিযোগী। আমাদের ঠিকানা বদল হয়েছে। এখন থেকে আমার বিনামূল্যে প্রাপ্য সংখ্যা ডাকযোগে বক্সিরহাটে পাঠালে বাধিত হব। বাড়ির নম্বর হল…
আমাদের সঠিক ঠিকানা না দিয়ে পাশের দোকানের ঠিকানা জানালাম যাতে করে পত্রিকা আব্বার হাতে না পড়ে। প্রতি মাসে আমরা সেই বিনামুল্যের সংখ্যার অপেক্ষায় বসে থাকতাম। এবং এই পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে স্বপ্নের মতো কাজ করেছিল।
তুলনামূলকভাবে পাঠ্যপুস্তক অবহেলা করা সত্ত্বেও এই পাঠ্যক্রম বহির্ভূত পড়াশুনোর জন্য প্রতিবছর ক্লাসে আমাদের ফল ভালই হত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে প্রায় প্রতিবারই আমি ক্লাসে প্রথম হয়ে এসেছি।
সাম্প্রতিক বিষয় সম্বন্ধেও আমরা ওয়াকিবহাল থাকতাম। এর জন্য বড়দা ও আমি প্রতিদিন আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডা. রসিকলাল বণিকের চেম্বারে বিভিন্ন সংবাদপত্র পড়ে সময় কাটাতাম।
…
প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকার পর ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট মধ্যরাত্রে।
এই সময় ভারতের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিকে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবিতে ‘পাকিস্তান-আন্দোলন’ তুঙ্গে উঠেছিল। আমরা জানতাম চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্গত হবে কারণ পূর্ব বাংলায় মুসলমানই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। বাংলার আর কোন কোন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্গত হবে বা সত্যিকারের সীমারেখা কোথায় টানা হবে তা তখনও স্থির হয়নি।
স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সম্ভাবনা হলে, তা ঠিক কখন হবে? এই নিয়ে ২০ নং বক্সিরহাট রোডে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ক্রমাগত তর্ক ও বাদানুবাদ চলতে লাগল। আমরা বুঝতে পারলাম তা হবে একটি রোমাঞ্চকর দেশ যার পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ড হাজার মাইলেরও বেশি ভারতীয় ভূখণ্ড দিয়ে বিভক্ত।
পূর্বাংশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এলাকা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল যা পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকার ৬ ভাগের এক ভাগ। পূর্ব অংশে প্রধানত নিচু সমতলভূমি, যাকে নানা ভাগে ভাগ করেছে অসংখ্য নদী, খাল, বিল, হ্রদ ও জলাভূমি। এখানে জমি এতই নিচু যে সমুদ্রের একশো মাইল দূরেও তা জলস্তরের চেয়ে মাত্র ৩০ ফুট উঁচু।
আমার আব্বা একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও তাঁর বহু হিন্দু বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন (নিশিকাকা, নিবারণকাকা, প্রফুল্লকাকা ও আরও অনেকে)। ছোট হলেও আমি বেশ বুঝতাম ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু ক্ষোভ ও অবিশ্বাস জমা হয়েছে। সংবাদপত্র পড়ে ও রেডিও শুনে আমরা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার খবর জেনেছি। ভাগ্যবশত চট্টগ্রামে তার খুব সামান্য আঁচ লেগেছিল।
কোনদিকে আমাদের রাজনৈতিক ঝোঁক এ ব্যাপারে কারওর কোনও সন্দেহ ছিল না। আমরা সবাই আন্তরিকভাবে ভারতের বাকি অংশ থেকে আলাদা হতে চাইছিলাম। আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট ভাই ইব্রাহীমের যখন বুলি ফুটল সে তার পছন্দের সাদা চিনিকে ‘জিন্না চিনি’ ও অপছন্দের গুড়কে ‘গান্ধী চিনি’ বলে ডাকতে শুরু করল।
মা পর্যন্ত তাঁর সান্ধ্যকালীন রূপকথার গল্পে জিন্না, গান্ধী ও মাউন্টব্যাটেনের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন যাতে আমরা বুঝতে পারি আমাদের জীবনে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।
আমার বড়দা সালাম, যদিও তার বয়স তখন মাত্র দশ, একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সংবাদ সংগ্রাহক হয়ে উঠল-যা সে আজ অবধিও আছে। স্থানীয় বড় ছেলেরা চাঁদ তারা আঁকা সবুজ পতাকার নীচে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ ধ্বনি দিতে লাগল-তাদের দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছিল।
এই সব আশা ও স্বপ্ন যে-রাতে শেষপর্যন্ত সত্যি হল সে সময়টা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে- যেন গতকালেরই ঘটনা।
দেখতে পেলাম আমাদের বাড়িটা পতাকা ও সবুজ-সাদা ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়েছে। সমস্ত পাড়া, এককথায় পুরো শহরটারই সাজ সাজ রব। বাইরে আমরা জ্বালাময়ী রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রায়শই তা চাপা পড়ে যাচ্ছিল ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ সোচ্চার ধ্বনিতে। তখন মধ্যরাত, কিন্তু পথে ভর্তি লোকজন যেন একটা হলঘর। ছাদ থেকে আমরা বাজি পোড়াচ্ছিলাম, অন্যদেরও তাই করতে দেখলাম। চারিদিকে প্রতিবেশীদের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম যাঁরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ফানুসের ও হাউইয়ের আলো ও বিস্ফোরণ দেখছিলেন। সারা শহর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল। রাতের আকাশ উজ্জ্বল রঙে সজীব হয়ে উঠেছিল।
মাঝরাতে আব্বা আমাদের নীচে রাস্তায় নিয়ে গেলেন। তিনি কোনওদিনই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না। কিন্তু ঐক্য ও সংহতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য মুসলিম লিগের ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই রাতে তিনি গর্বভরে ন্যাশনাল গার্ডের পোশাক পরলেন, এমনকি জিন্না টুপি পর্যন্ত। আমার ভাইবোন দুই বছরের ইব্রাহীম ও ছোট্ট টুনুও আমাদের সাথে ছিল। ঠিক মাঝরাতে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থগিত হল। গোটা শহর অন্ধকারে ডুবে গেল। পরমুহূর্তে আলো জ্বলে উঠল। একটি নতুন দেশের জন্ম হল।
‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগানে বার বার সোচ্চার হয়ে উঠল চট্টগ্রামের প্রতিটি অঞ্চল। সাত বছর বয়সে এই প্রথম আমি দেশবাসীর জন্য প্রতিটি শিরায় গর্ব ও উম্মাদনা অনুভব করলাম।
আরও অনেক কিছু তখনও ঘটতে বাকি ছিল।
#লেখাটি- বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল লরিয়েট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন থেকে নেওয়া। বইটির প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ – ২০০৪ খ্রি.