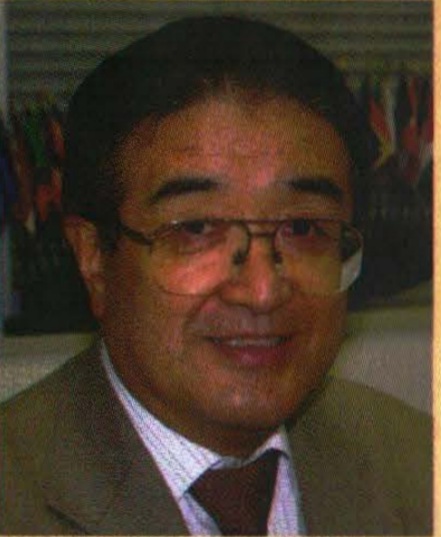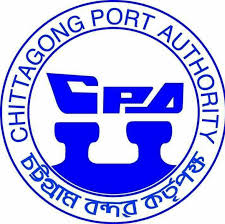চট্টগ্রাম ২৬ মার্চ, ২০২৫:
‘এখন রাত দুটো। প্রচণ্ড গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।’
নির্জন বাড়িতে সোফায় বসে মি. কে টেপরেকর্ডার চালিয়ে এভাবে ধারাবর্ণনা দিতে শুরু করলেন। তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্য প্রবাসীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে সরকারের পাঠানো জাপান এয়ারলাইনসের বিমানে ১৩ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেছেন। মি. কে সাধারণত টেপরেকর্ডারটি ব্যবহার করে থাকেন তাঁর প্রিয় জাপানি পুরোনো পপ গান ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের যুদ্ধের গান শোনার জন্য। কিন্তু আজ তিনি তাঁর আশপাশের ঘটনাবলি এতে রেকর্ড করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর টেপ থেকে কামানের পর মেশিনগানের শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গে পথচারীদের চিৎকারও। তারপর তিনি বলতে শুরু করেন, ‘বাঙালি ও সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হতে পারে ভেবে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন ছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেটি সত্যি সত্যিই ঘটল।’
গত কয়েক দিনে পাকিস্তানি সেনাদের শক্তি যেভাবে বাড়ানো হয়, সেটি ছিল সত্যিই চোখে পড়ার মতো। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে দুই ডিভিশনের অধীনে প্রায় ৪০ হাজার সেনা মোতায়েন ছিল। এখন সেনার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চারটি ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেড মিলে ৯০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের সরকারি বিমান সংস্থা পিআইএ বিরামহীনভাবে পশ্চিম থেকে উড়ে এসে ঢাকায় সেনা নামিয়েছে। সেনাদের পরনে ছিল সাদা পোশাক।
ঢাকায় আসার পথে শ্রীলঙ্কায় জ্বালানি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে এবং ঢাকা বিমানবন্দরে বাঙালি ও বিদেশি সাংবাদিকদের অপ্রয়োজনে প্ররোচিত করার বিপদ এড়ানোর জন্য তাদের সাদা পোশাক পরার নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয় যে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্বের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠানে যে রাজি হয়েছিল, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল বেশি সংখ্যায় সেনা পাঠানোর জন্য সময় নেওয়া।
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে বাঙালি এমনিতেই কম। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক পরিবহন, যোগাযোগ ও নির্মাণ ইউনিটের মতো বিভাগে নিয়োজিত। আবার তাদের মোতায়েন করা হয়েছে কাশ্মীর ও পেশোয়ারের মতো পশ্চিমের রণক্ষেত্রে। এর আগে ব্রিটিশ আমল থেকে সুদীর্ঘ ইতিহাসসংবলিত দুটি রেজিমেন্ট ছিল। একটি হলো ১৫ হাজার সেনা নিয়ে ইপিআর বা পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, অন্যটি ইবিআর বা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, যার সেনাসংখ্যা ২০ হাজার। এসব বাঙালি সেনা পুলিশ বাহিনীর এক অংশের সঙ্গে সহযোগিতা করে পশ্চিমের সামরিক বাহিনীর দমন অভিযানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।
ঢাকায় জাপান কনস্যুলেট জেনারেলের অ্যাটাসে মি. আরাকির কথায়, ‘আমি থাকি ইপিআরের সদর ঘাঁটির কাছে। তাদের হাতে অস্ত্র বলতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বাহিনীর ব্যবহার করা পাঁচ গুলিঅলা টম্পসন সাবমেশিনগান ছাড়া বিশেষ কিছুই ছিল না। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। বাঁ দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাধুনিক মেশিনগান থেকে অনবরত গুলি চালানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম। এদিকে ডান দিক দিয়ে ইপিআরের চালানো খণ্ড খণ্ড রাইফেলের গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।’
এই সংঘর্ষের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে বাঙালি সেনাদের কাছে দেশের চেয়ে জাতিগত পরিচয়টা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ সংঘর্ষের ফলে যে তাদের অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
রেডিও পাকিস্তানের ২৬ মার্চের দুপুরের খবরে সামরিক আইন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের এক নির্দেশ জারি করা হয়:
‘পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ এলাকা এখন স্থলবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সব গণমাধ্যমকে হয় সামরিক বাহিনীর সরাসরি অধীনে অথবা সেন্সরের অধীনে রাখা হবে। যেসব শ্রমিক কর্মবিরতি পালন করেছে, সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের কর্মস্থলে ফিরে আসতে হবে।’
রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রেডিওর মাধ্যমে ভাষণ দেন। ইংরেজি ও উর্দুতে দেওয়া ২০ মিনিটের এই ভাষণে ছিল ক্ষোভ ও অভিমানের সুর:
‘শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বললাম, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলন মুসলিম দেশ পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছু
নয়। আওয়ামী লীগকে এখন বেআইনি ঘোষণা করা হলো। প্রকৃতপক্ষে আরও কয়েক সপ্তাহ আগেই শেখ মুজিব ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল…।’
পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান ও পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানোর মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শেষ হয়।
২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় নিযুক্ত তৎকালীন জাপানি কনসাল জেনারেল মাসাতাদা হিগাকি নিমন্ত্রিত হয়ে মার্কিন কনসাল জেনারেল হার্বার্ট স্পিভাকের বাসভবনে গিয়েছিলেন। বিদেশি কূটনীতিকেরা চলমান কঠিন পরিস্থিতির কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থেকে যাতে আনন্দময় সময় কাটাতে পারেন, সে জন্য
মি. স্পিভাক সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকেরা একসঙ্গে বসে মার্কিন অভিনেত্রী লানা টার্নার অভিনীত পুরোনো দিনের রোমান্টিক ফিল্ম উপভোগ করছিলেন।
রাত ১১টার দিকে, কাহিনিটা যখন শেষ পর্যায়ে, মি. স্পিভাকের একজন সচিব এসে তাঁর হাতে একটা স্লিপ দিলেন। মি. স্পিভাক চুপচাপ পাশের ঘরে গিয়ে তারপর আবার এসে আসরে উপস্থিত হলেন। বললেন, ‘ভদ্রমহোদয়গণ, মনে হচ্ছে বাইরের পরিস্থিতি অনুকূল নয়, সিনেমা মাঝখানে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, আপনাদের সবার এক্ষুনি নিজ নিজ বাসায় চলে যাওয়া উচিত হবে বলে মনে হয়।’
কথাটা শুনে হঠাৎ যেন সবার ঘুম ভেঙে গেল। সবাই তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।
কনসাল জেনারেল হিগাকি যে বাড়িতে থাকতেন, সেটি মার্কিন কনসাল জেনারেলের সরকারি বাসভবনের একদম কাছে। সাধারণত গাড়িতে করে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। কিন্তু সেদিন এই পথটুকু যেতে আধঘণ্টা লেগেছিল। গাড়ির চলাচল বিঘ্নিত করতে রাস্তার এখানে-সেখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ধানমন্ডির বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক বুকে লাগিয়ে যুবকেরা দ্রুততার সঙ্গে অবরোধ সৃষ্টি করছিল। মি. হিগাকির গাড়ি দেখে তারা ভদ্রতার সঙ্গে বিকল্প রাস্তা দেখিয়ে দিল।
মি. হিগাকির পরিবার ইতিমধ্যে ১৩ মার্চ বিমানযোগে জাপানে ফিরে যাওয়ায় বিশাল বাসভবনটা খাঁ খাঁ করছিল।
তিনি যখন স্নান করতে শুরু করলেন, তখন বাথরুমের দরজা সজোরে আঘাত করে তাঁর চৌকিদার চেঁচিয়ে উঠল, ‘হুজুর, বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে!’
মি. হিগাকি গায়ে গাউন চাপিয়ে ছাদে উঠলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঢাকা শহরের কোনো কোনো স্থান থেকে হিংসাত্মক পরিস্থিতি উপলব্ধি করা গেলেও গুলির আওয়াজ শুনতে পাননি তিনি।
‘আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তুমি ভুল শুনেছ।’ বলে মি. হিগাকি সিঁড়ি দিয়ে যখন নামতে শুরু করলেন, তখন হঠাৎ তিনি গুলি এবং রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পান। সেই সঙ্গে তাঁর কানে এল ‘জয় বাংলা! জয় বাংলা!’ বলে চিৎকার, যা এসেছিল তাঁর পাশের বাড়ি থেকে। তিনি সেই কণ্ঠস্বরের মালিককে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন-স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান।
এই রাতে পাকিস্তানি বাহিনী শেখ মুজিবের বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। বাড়িতে তাঁর পরিবারের সঙ্গে রয়ে যায় একটি ছোট্ট বানর। বানরটিকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। পরে এই বানর পোষার দায়িত্ব নিলেন মি. হিগাকি।
আওয়ামী লীগের ঢাকা অঞ্চলের একজন নেতা আবদুল আহমেদ সেদিনের কথা স্মরণ করে বললেন, ‘২৫ তারিখ রাতে আমি শেখ মুজিবের সঙ্গে ছিলাম। সেদিন তাঁর বাসায় আসা অতিথিদের নয়টার মধ্যে বিদায় দিলেন এই বলে যে সাধারণ নাগরিকেরা স্বাধীন বাংলা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য প্রাণ দিতে হতে পারে। কিন্তু এটাই হবে আমাদের শেষ আত্মত্যাগ।
‘শান্তি প্রতিষ্ঠার পর এমন বুলি আর কখনো দিতে হবে না।… শেখ মুজিবের এই উক্তি সম্ভবত এমন ইঙ্গিত বহন করছিল যে সে রাতে কী ঘটতে যাচ্ছিল, তিনি সেটা জানতেন। দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদসহ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের কাউকেই সেদিন দেখতে পাওয়া যায়নি।’
আসলে তাজউদ্দীন আহমদরা ততক্ষণে যশোরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং ৩০ মার্চ ভোর হওয়ার আগেই ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। এদিকে পাকিস্তানি সেনারা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করার পর বাঙালিদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সারা দেশে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল।
পাকিস্তানি সেনারা প্রথমে হামলা চালিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পূর্ব পাকিস্তানে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময়ই নেতৃত্ব প্রদান করে এসেছে। ২৬ মার্চের ভোরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সেনাবাহিনী প্রবেশ করে এবং ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মচারীদের লক্ষ্য করে নৃশংসভাবে গুলি চালায়।
বাংলা বিভাগের ছাত্র রফিক, পরে মুক্তিবাহিনীর হাতিয়া অঞ্চলের কমান্ডার হয়েছিল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র শাহজাহান, পরে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছিলেন, তারা তখন হলের দোতলায় ছিল।
পরে শাহজাহানের কাছ থেকে শোনা সেদিনের ঘটনা এ রকম, ‘তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রী ছিল। ছাত্রদের কাছে কয়েক ডজন রাইফেল লুকিয়ে রাখা থাকলেও প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেখান থেকে পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমার একজন সহপাঠী আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জানানোর জন্য মাথার ওপরে হাত তুলে তাদের সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার চোখের সামনে পাকিস্তানি সেনারা গুলি চালিয়ে আমার বন্ধুকে মেরে ফেলেছিল। আমি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে পালিয়ে কোনো রকমে বেঁচে গেলাম।’
রফিক তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছে, ‘সেনাদের আসতে দেখে আমি দোতলা থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে গেলাম। তাদের হাতে ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্র। ভাবলাম, ওদের সঙ্গে লড়া মানে সঙ্গে সঙ্গে মরা। তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো মানে হয় না।’
সেই ঘটনার দুই দিন আগেই নূরে আলম সিদ্দিকীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নেতারা গা-ঢাকা দিয়েছিল।
এই হামলার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও পাকিস্তানি সেনাদের মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সেদিন ক্যাম্পাসে ছিল না।
স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য ছাত্রদের দাবি বন্দুকের সামনে একসময় অনর্থক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আসলে সেনা মোতায়েনের ফলে ছাত্রদের বিক্ষিপ্ত আন্দোলন একসূত্রে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। ছাত্ররা সবাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঝান্ডার নিচে একত্র হলো। পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে অনেকেই ঢাকার বাইরে চলে গিয়ে ইপিআর ও ইবিআরের সেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে মুক্তিবাহিনী গঠন করে এবং বাহিনীর নেতা হিসেবে কাজ শুরু করে।
নৃশংস হত্যাকাণ্ড-২৭ মার্চ ১৯৭১-
মি. কের রেকর্ড করা বক্তব্য এ রকম:
‘সকাল সাতটায় সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়া হলে তাৎক্ষণিকভাবে রাস্তায় গাড়ি ও লোকজনের চলাচল শুরু হয়। ঢাকা শহরের পরিস্থিতি দেখার জন্য আমিও বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। দেখলাম, সামান্য আসবাবপত্র-বাসনকোসন নিয়ে এবং পাঁচ-ছয়টি বাচ্চা সঙ্গে করে বেশ কয়েকটি পরিবার শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হয়তো ঢাকা নিরাপদ নয় ভেবে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে চলেছে।
‘পাকিস্তানি সেনাদের এবারের দমনাভিযান আসলে উন্মাদনায় ভরা। তারা নিরস্ত্র বেসামরিক লোকজনের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে শুধু তারা ক্যান্টনমেন্টের কাছে থাকে বলে। ছাত্র আন্দোলন বা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোককে দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করেছে। আবার তারা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামলা চালিয়ে নার্স, এমনকি রোগীদের পর্যন্ত গুলি করে অথবা পুড়িয়ে মেরেছে।
‘এসব কাণ্ড দেখে আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলাম। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে যে গভীর কষ্ট ও ক্ষোভ রয়েছে, সে কথা অনায়াসে অনুমান করা যায়। পাকিস্তান নাকি বিশ্বব্যাংকসহ সাহায্যদানকারী দেশগুলোর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানানোর পরিকল্পনা করছে। তবে এ রকম অমানবিক কার্যকলাপের পর চীন ছাড়া অন্য কোনো দেশ কি তাতে সাড়া দেবে? পূর্ব পাকিস্তানে ইতিমধ্যে এক লাখের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বলে গুজব রয়েছে। দিন দিন মৃত ও আহতের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এমন কথাও শুনতে পাচ্ছি যে সেনাবাহিনী কালো তালিকা বানিয়ে সেই অনুযায়ী হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।
‘ঢাকা শহরে মেশিনগান হাতে সেনাবোঝাই ট্রাকগুলোকে রাস্তায় চলাচল করতে দেখা যায়। সেনারা দিনের বেলায় গুলি চালানো থেকে বিরত থাকে।
কিন্তু সন্ধ্যা ছয়টার পর সান্ধ্য আইন জারি হলে তারা যেন চাঙা হয়ে ওঠে। তারা নাকি লোকজনকে এমনভাবে হত্যা করে যেন খরগোশ বা বিড়াল মারছে। এমন দৃশ্যের কথা ভেবে ক্ষোভে ও দুঃখে গা শিউরে ওঠে।
‘আমার মনে হয় না জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট, সেই সঙ্গে বিশ্বের নানা দেশ পাকিস্তানের কর্মকাণ্ড দেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু যতটা সম্ভব দ্রুত পাকিস্তান সরকারকে চাপ দেওয়ার মাধ্যমে এই নৃশংস কাজ বন্ধ করানো প্রয়োজন। গত বছর আগস্টের ব্যাপক বন্যা, নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এবং এবারের হত্যাযজ্ঞের ফলে পূর্ব পাকিস্তান বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে যাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন, তাঁদের মন অবশ্যই দুঃখে ভরা থাকবে।
‘বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তাগিদে অনেক দেশেই নাগরিকদের রক্তে মাটি ভিজে গেছে। মানবজাতি কি এই বাংলার মাটিতে আবার সে রকম ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখতে যাচ্ছে?
‘অন্যদিকে আমি নিজে জাপানি হয়ে জন্মানোর জন্য গভীরভাবে গর্ব ও আনন্দ বোধ করছি।
‘দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে মাত্র ২৫ বছরে জাপান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে পেরেছে। আমার মনে হয়, উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে পাকিস্তানের মতো দেশের মানুষের কাছে জাপানের সাফল্য স্বপ্নের মতো মনে হবে।’
জনশূন্য বিশাল বাসভবনের ড্রয়িংরুমে একলা বসে মি. কের মন এ রকম নানা ভাবনায় ভরে গিয়েছিল।
চট্টগ্রামে সংঘর্ষ
১৬ এপ্রিল ১৯৭১ পর্যন্ত কয়েক দিনের ঘটনাবলি:
২৬ মার্চ সারা দিন চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করা ওয়াকাসামারু জাহাজের নাবিকদের কানে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসে। সেদিন রাত ১১টায় ওই জাহাজ থেকে ৫০০ মিটার দূরে পাকিস্তানি নৌবাহিনী আলো বিচ্ছুরণকারী কামানের গোলা বা ট্রেসার শেল ছুড়তে শুরু করে। তা দেখে ক্যাপ্টেন ইতো সব নাবিককে জাহাজের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার আদেশ দেন। বিদ্যুৎ চলে গিয়ে সারা চট্টগ্রাম শহর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। শুধু বন্দরে থাকা আটটি দেশের ১৩টি জাহাজে আলো দেখা যাচ্ছিল।
বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত জেলা আদালতের ইটের ভবনকে ঘাঁটি করা পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে তারা তিন দিক থেকে গুলিবর্ষণ করেছিল। তাদের মধ্যে ছিল মেসবাহ্, যার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে রেডক্রসের সহকর্মী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। তখন সে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনা করছিল। সেই দিন মেসবাহ্ পাহাড়ের নিচে থাকা মসজিদে মর্টার কামান বসিয়ে আক্রমণে অংশ নিচ্ছিল।
চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনীর একটি অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান। তিনি কালুরঘাট রেডিও স্টেশন এলাকা থেকে নির্দেশ প্রদান করছিলেন।
২৭ তারিখ বেলা ১১টা ২০ মিনিটে ওয়াকাসামারুর কাছে নোঙর করা পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ থেকে হঠাৎ ছয়জন বাঙালি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরের মুহূর্তে তাঁরা গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। পরে জানা গেছে, তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে জাহাজে চড়ে অগ্নিসংযোগ করতে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।
একই দিন ঢাকায় জাপানি কনসাল জেনারেল মাসাতাদা হিগাকি সামরিক আইন কমান্ডার টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর আগের দিন সেনারা কনস্যুলেট জেনারেলের চত্বরে প্রবেশ করে কর্মচারীদের ভয় দেখান। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানানোর জন্য এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
২৯ মার্চ দুপুরের দিকে চট্টগ্রাম বন্দরে বাইনোকুলারের সাহায্যে ক্যাপ্টেন ইতো তিনটি মৃতদেহ ভেসে আসতে দেখেন। কিন্তু তিনি সে কথা কাউকে বলেননি। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, খবরটি শুনে নাবিকেরা ভয় পেয়ে যাবেন। তিনি ভেবেছিলেন, এমন পরিস্থিতির মধ্যে নাবিকেরা যাতে বিচলিত না হন অথবা তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা অথবা তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মি. ইতো নাবিকদের বলেন, ‘আমাদের জাহাজ থেকে যেসব টেলিগ্রাম পাঠানো হবে, সেগুলো সম্বন্ধে তোমরা অবহিত থাকবে। তোমরা যদি তোমাদের আত্মীয়স্বজনকে টেলিগ্রাম পাঠাতে চাও অথবা তাদের কাছ থেকে পেতে চাও, তাহলে তাতে কোনো বাধা থাকবে না। আমাদের জাহাজে যে পরিমাণ খাবার ও পানি রয়েছে, তা দিয়ে ৪০ দিন চালানো সম্ভব। আবার যে পরিমাণ চাল বোঝাই করা আছে, তা খেয়ে ৫০ বছর কাটিয়ে দিতে পারব। অন্যান্য খাবারেরও কোনো অভাব নেই। তাই আমরা উপাদেয় খাবার খেয়ে আনন্দ করব। সমস্যা হলো মদ ও সিগারেট নিয়ে; কারণ, আমাদের জাহাজ যেদিন চট্টগ্রাম বন্দরে ঢুকেছিল, সেদিন শুল্ক বিভাগের লোকজন এসে এক সপ্তাহ ব্যবহারের মতো মদ ও সিগারেট বাদে বাকি সবকিছুর ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সেগুলোর ওপর সিল লাগিয়ে দিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তোমাদের যদি এ দুই জিনিসের অভাব হয়, তবে সিল খুলে ফেলতে পারো। তার জন্য ফাইনের টাকা আমি দিয়ে দেব।’
এদিকে ঢাকায় মি. কে চট্টগ্রাম থেকে ভেসে আসা রেডিও তরঙ্গ শুনতে পেরেছিলেন।
তাতে মেজর জিয়াউর রহমান পাকিস্তান সরকারের হাতে আটক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে লোকজনকে সাহস জুগিয়েছিল।
এদিন বেলা দুইটা ২০ মিনিটে পাকিস্তানি বিমানবাহিনী তাদের অতি মূল্যবান দুটি এফ-৮৬ যুদ্ধবিমান চট্টগ্রামে পাঠায়। একই সঙ্গে বন্দরের বাইরে নোঙর করা দুটি ডেস্ট্রয়ার থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বেতার কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে কামান দিয়ে হামলা শুরু করে।
ওয়াকাসামারুর চারপাশে একের পর এক মৃতদেহ ভাসছিল। শেষ পর্যন্ত তার সংখ্যা ৩০-এ দাঁড়ায়। ক্যাপ্টেন ইতো জাহাজ কোম্পানির সদর দপ্তরে পাঠানো টেলিগ্রামে উল্লেখ করেছিলেন যে চট্টগ্রাম বন্দরের দৃশ্য আগের বছর কম্বোডিয়ার নমপেনে ঘটে যাওয়া প্রবাসী ভিয়েতনামিদের গণহত্যার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।
ওয়াকাসামারুর সামনে একটি ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ নোঙর করে ছিল। ৩১ তারিখে ক্যাপ্টেন ইতো সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে যান তথ্য বিনিময়ের জন্য।
ব্রিটিশ জাহাজটিতে মিঠা পানির অভাব দেখা দিচ্ছিল। পানির দৈনিক ব্যবহার নাবিকপ্রতি এক বালতির দশ ভাগের আট ভাগ পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়। এটুকু পানি দিয়ে হাতমুখ ধোয়া ও কাপড় কাচাসহ সব কাজ করতে হয়।
ব্রিটেনের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জাহাজটিকে আদেশ দিয়েছে চট্টগ্রামে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্য থেকে মহিলা, শিশুসহ ৬০ জনকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য। ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেন মি. ইতোর সামনে চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ‘আমার জাহাজ গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা বহন করে বের হলে কেউ ঠেকাতে পারবে না। এ ছাড়া আমার সাহায্যের ডাক শুনলে ভারতের বিশাখাপত্তম সামরিক বন্দর থেকে ব্রিটেনের রাজকীয় নৌবাহিনী ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ছুটে আসবে। চট্টগ্রাম বন্দর আমার নখদর্পণে।
আপনি না হয় আমার পেছন পেছন চলে আসুন, তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবেন।’
ক্যাপ্টেন ইতো এর আগে পাঁচবার এ বন্দরে এসেছিলেন। কিন্তু এবার বন্দরে প্রবেশ করলেন ১১ বছর পর। যুদ্ধকবলিত এ বন্দর থেকে একা বের হওয়া তাঁর কাছে কঠিন মনে হলো। তাই তিনি মনস্থির করলেন, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ব্রিটিশ জাহাজকে ভর করেই এখান থেকে পালাতে হবে।
বন্দরটির বাইরে থাকা পাকিস্তানি জাহাজ থেকে কামানের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। স্রোতে ভেসে এসে বাঙালিদের ৫০টির বেশি মৃতদেহ ওয়াকাসামারু জাহাজের পাশে জমা হয়েছে। চারদিক অসহ্য রকমের দুর্গন্ধে ভরপুর। সেই গন্ধের কারণে অসংখ্য মাছি ও কাক জড়ো হচ্ছে মৃতদেহের ওপর। কোনো কোনো কাক সেগুলো থেকে মাংসের টুকরো নিয়ে ওয়াকাসামারু জাহাজের ওপর বসে খাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে সবাই ভীষণ কষ্ট পেল। জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে মৃতদেহগুলো সমাহিত করতে চাইলেও পাকিস্তানি সেনাদের ভয়ে কাজটি করা সম্ভব হয়নি।
লেখক:তাদামাসা হুকিউরা।
তাঁর জন্ম ১৯৪১ সালের ১৭ মার্চ উত্তর জাপানের আকিতা জেলার প্রধান শহর আকিতায়। টোকিওর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। সাইতামা জেলা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে টোকিও-ভিত্তিক বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইউরেশিয়া ২১ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় শরণার্থীদের সাহায্য দেওয়ার কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ডুনান্ট, বিশ্বে শরণার্থীসহ অনেক বইয়ের লেখক তিনি। বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে গবেষণা করেন।
তার গ্রন্থ ‘রক্ত ও কাদা ১৯৭১’ থেকে লেখাটি তুলে ধরা হয়েছে। এটি ২০১২ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত।