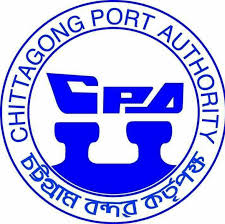চট্টগ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪:
ভূমিকা
লেখাটি গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের গ্রন্থ ‘বাঙলার গাছপালা’র ‘মশক নিধনে জলজ উদ্ভিদের অপূর্ব প্রভাব’ অধ্যায়। প্রয়াত বিজ্ঞান সাধক ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণের উপযোগী বহু প্রবন্ধ বাংলায় লিখেছেন। একজন বাঙালি পতঙ্গবিশারদ ও উদ্ভিদবিদ, যিনি সামাজিক কীটপতঙ্গের ওপর তার গবেষণাকর্মের জন্য বিখ্যাত।১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের পয়লা আগস্ট বাংলাদেশের শরিয়তপুরের নড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে টেলিফোন অপারেটর হিসেবে কাজ করার সময় প্রবাসী পত্রিকায় জৈবদ্যুতি নামক তার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তা জগদীশচন্দ্র বসুর নজরে আসে। জগদীশচন্দ্র তাকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে মেরামতির কাজে নিযুক্ত করেন। এই প্রতিষ্ঠানে থেকেই তিনি জীববিদ্যার ওপর গবেষণা শুরু করেন।
##বছর কয়েক পূর্বে মশকভুক মাছ নিয়া পরীক্ষা করেছিলাম। খসে, পুঁটি, তেচোখা, চাঁদা, তেকাঁটা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ এবং শাল, শোল বোয়াল প্রভৃতি মাছের ছোট ছোট বাচ্চাগুলি সকলেই কম-বেশী মশার বাচ্চা উদরস্থ করে থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখেছিলাম, আমাদের দেশীয় পাতি-চাঁদা এবং কোলা-ব্যাঙের ব্যাঙাচিগুলিই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মশক-শিশু উদরস্থ করে থাকে। অবশ্য এই মশক-ধ্বংসের পরিমাণ অনেকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মশক-দমনে সাধারণতঃ তেচোখা মাছের কৃতিত্বের বিষয়ই বিশেষভাবে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তেচোখা মাছগুলি সর্বদাই জলের উপরিভাগে ভেসে থাকে বলে মশক-শিশুর প্রাচুর্য থাকলেও অনেকেই তারা মাছের নজর এড়িয়ে আত্মরক্ষা করে থাকে। বাতাস গ্রহণ করবার জন্য মশার বাচ্চাগুলি জলের উপরিভাগে উঠে আসবার সময় দৈবাৎ নজরে পড়ে গেলেই কেবল তারা তেচোখা মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বাচ্চাগুলি জলের উপরে উঠেই নীচু দিকে মুখ করে নির্জীব খড়কুটার মত ঝুলে থাকে; কাজেই অনায়াসেই মাছের নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু চাঁদা, খলসে প্রভৃতি মাছেরা জলের মধ্যে বিচরণ করে। কিলবিল করে উপরে ওঠবার সময় বেশ দূর থেকেও মশার বাচ্চাগুলি তাদের নজরে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ এসে উদরসাৎ করে ফেলে। বিভিন্ন জাতীয় মাছের মশার বাচ্চা উদরস্থ করবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে ছোট বড় অনেকগুলি কাচের জলাধারে মাছ ও মশার বাচ্চা রেখে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। দেখলাম-প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই একটা জলাধারের পাঁচটা চাঁদা মাছ ছিয়াশিটি মশক-শিশু উদরস্থ করে ফেলল কিন্তু অপর একটি জলাধারে সমানসংখ্যক তেচোখা-মাছেরা ঐ সময়ের মধ্যে বার- তেরটির বেশী মশার উদরস্থ করতে পারে নাই। মাছ ও মশার বাচ্চাগুলি স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে বলে কতকগুলি জলাধারে জলঝাঝি, পাটা শ্যাওলা এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার জলজ উদ্ভিদ রেখেছিলাম কিন্তু ঘোলা জল এবং লতাপাতার প্রতিবন্ধকতার জন্যই খুব সম্ভব ঐ সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ সন্তোষজনক হয় নাই। বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি জলাধার রাখা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ছয়টি ছিল-জলজ উদ্ভিদপরিপূর্ণ; কিন্তু বাকী সবগুলিতেই পরিষ্কার জলে মশার বাচ্চা কিলবিল করছিল। পরীক্ষার জন্য একবার সময়মত মৎস্য সংগ্রহ করতে না পারায় জলজ- উদ্ভিদপূর্ণ জলাধার থেকে মাছগুলি তুলে এনে পরিষ্কার জলাধারে ছেড়ে দিয়েছিলাম। লতাপাতাপূর্ণ জলাধারগুলিতে যে-সকল মশার বাচ্চা ছেড়েছিলাম সেগুলি তেমনই রয়ে গেল। তিন-চার দিন পর নজর পড়তেই দেখলাম-জলজ উদ্ভিদ- পূর্ণ জলাধারগুলিতে মশার বাচ্চার সংখ্যা যেন কম বোধ হচ্ছে। আরও কয়েক দিন পরে ঐ সকল জলাধারে কচিৎ দুটি-একটি ছাড়া মশার বাচ্চা দেখতেই পেলাম না। এতগুলি মশার বাচ্চা কিরূপে অদৃশ্য হল বুঝতেই পারলাম না; কারণ এর কোনটিতেই একটিও মাছ ছিল না। এতগুলি বাচ্চা যে মশার রূপ ধারণ করে উড়ে পলায়ন করেনি তা সুনিশ্চিত। কারণ-ট্যাঙ্কগুলির মুখ পাল্লা জালে আচ্ছাদিত ছিল। তার পর আরও কয়েকবার এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি। অনাবৃত জলাধারগুলি পাশাপাশি সজ্জিত রয়েছে। পরিষ্কার জলে মশার বাচ্চা কিলবিল করছে অথচ জলজ উদ্ভিদপূর্ণ জলাধারে মশার বাচ্চা নজরে পড়ে না। তবে কি জলজ উদ্ভিদপরিপূর্ণ জলাধারে মশকেরা ডিম পাড়ে না? ব্যাপারটায় যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার হলেও মশকভুক মাছ সম্বন্ধে পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকায় এ বিষয়ে তেমন কিছু মনোযোগ দিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে কোলা-ব্যাঙের ব্যাঙাচির মশক-শিশু ভক্ষণের ব্যাপার অকস্মাৎ নজরে পড়ে। এই ব্যাঙাচির জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় সম্যক্ অবগত হবার জন্য বহু স্থানে নালা, ডোবা ও অন্যান্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী জলাভূমিসমূহ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। এই সময়ে মশার বাচ্চার উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে অনেকগুলি অদ্ভুত বিষয় নজরে পড়ে। পূর্বোক্ত পরীক্ষার সময় জলজ-উদ্ভিদপূর্ণ জলাধারে যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলাম, স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেও সেরূপ অনেকগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদ-বিবর্জিত পচা জল পরিপূর্ণ অস্থায়ী জলাশয়েই মশক-শিশুর প্রাবল্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিন্তু পাটা শ্যাওলা জলঝাঁঝি ও অন্যান্য বহুবিধ জলজ-উদ্ভিদপরিপূর্ণ অথবা সম্পূর্ণরূপে পানা জলাশয়ে মশার বাচ্চা এক প্রকার নাই বললেই চলে।
বিশেষ পরীক্ষাকার্যের প্রয়োজনে কিছুকাল পূর্বে পরীক্ষাগারে এক-কৌষিক আণবিক উদ্ভিদ ও সূত্রবৎ শৈবাল জাতীয় জলজ উদ্ভিদ জন্মাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। বড় বড় গামলা জলপূর্ণ করে তাতে নাইটেলা, কারা, হাইড্রিলা, ভেলেনেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ প্রতিপালিত হচ্ছিল। কিছু কাল পরে দেখা গেল কতকগুলি গামলায় উদ্ভিদগুলি স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও কয়েকটি গামলার উদ্ভিদ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সকল গামলায় উদ্ভিদগুলি প্রচুর পরিমাণে জন্মেছে তাতে একটিও মশার বাচ্চা নাই। কিন্তু যেখানে গাছগুলি মোটেই জন্মে নাই এবং যেখানে সেগুলি মরে পচে উঠেছিল তথায় প্রচুর পরিমাণ মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে। এই ঘটনা লক্ষ্য করবার পর এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে-দিনের বেলায় এই সকল জল-নিমজ্জিত উদ্ভিদ থেকে অনবরত সূক্ষ্ম সূক্ষ অসংখ্য বুদ্বুদ সূক্ষ্ম
সূত্রাকারে উপরে উঠে আসছে। এগুলি অক্সিজেন গ্যাসের বুদ্বুদ। আলোর প্রভাবে উদ্ভিদ-দেহে সংগঠন-উপযোগী খাদ্যবস্তু প্রস্তুতের সময় এই গ্যাস নির্গত হয়। অনেকবারই মনে হয়েছিল-এই অক্সিজেন কি মশার বাচ্চা নিয়ন্ত্রণে কোন প্রভাব বিস্তার করে থাকে? কিন্তু এরূপও ত হতে পারে যে ঐ সকল উদ্ভিদ থেকে কোন পদার্থ নির্গত হয়ে জলের সঙ্গে মিশ্রিত হবার ফলেই মশার বাচ্চাগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে জলজ-উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ কয়েকটি বদ্ধ জলাশয়ে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম সেখানে মশার বাচ্চার সন্ধান না মিললেও অন্যান্য জলজ কৃমি, কীটের অভাব ছিল না। কাজেই সন্দেহ করবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল যে, উদ্ভিদ থেকে কোন বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হলে সকল প্রকার কৃমি, কীটই বিনষ্ট হত। যাহোক, মশক নিয়ন্ত্রণে জলজ-উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা কে কি গবেষণা করেছেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে দেখতে পেলাম, নশক বিনাশের উপায় নিবারণকল্পে বিভিন্ন দেশের যে সকল বৈজ্ঞানিক, গবেষণা এবং অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত হয়েছেন তাঁদের অনেকেই বিশেষ কয়েক প্রকার জলজ-উদ্ভিদের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি সাধারণ পর্যবেক্ষণের পর্যায় অতিক্রম করে প্রকৃত গবেষণার ক্ষেত্রে অধিক দূর অগ্রসর হয়। অনেকেই জলজ-উদ্ভিদ সমন্বিত জলাশয়ে মশার বাচ্চার অভাব লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু এর বিপরীত ঘটনাও যে লক্ষিত হয় নাই – এমন নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বিশেষ বিশেষ জলজ-উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ জলাশয়ে সাধারণত মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে না অথবা জন্মগ্রহণ করলেও কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে যায়। পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার ফলে মশক-দমনে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে যতদূর জানতে পারা গেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে মশকের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ হলেও মশকেরা আমাদের সঙ্গে যে রূপ ভয়াবহ শত্রুতা সাধন করে থাকে তা কারও অবিদিত নয়। এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগের বীজাণুসমূহ বিভিন্ন জাতীয় মশক কর্তৃকই মনুষ্যশরীরে সংক্রামিত হয়ে থাকে। জীবজন্তুর কয়েকটি বিশেষ রোগও মশক কর্তৃক দেহান্তরে পরিচালিত হয়। কেবল রোগবীজাণু সংক্রমণের ব্যাপারই নয়, মশকের অভাবনীয় আধিক্যহেতু এদের দলবদ্ধ দংশন যন্ত্রণার ভয়ে বাসোপযোপী অনেক স্থান সম্পূর্ণ- রূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। অনুসন্ধানকারী এবং ভ্রমণকারীদের অনেকেই দলবদ্ধ মশকের ভীষণ আক্রমণের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এক সময়ে আমাদের দেশেও যে কোন কোন অঞ্চলে দলবদ্ধ মশক আক্রমণে লোকের জীবন বিপন্ন হত; এরূপ ঘটনার কথা বিরল নয়। মশকের যে ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু বহন করে একথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মানুষের অজ্ঞাত ছিল। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে সার রোনাল্ড রস্ তাঁর এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন যে,
ম্যলেরিয়া উৎপাদনকারী জীবাণুগুলি তাদের জীবনের মধ্যমাংশে মশকের দেহাভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। এই সময়ে মশক কর্তৃক দংশিত হলে রোগবীজাণু মনুষ্য দেহে সংক্রামিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে Culex pipiens নামক সাধারণত পরিচিত কেবলমাত্র এক জাতীয় মশার মোটামুটি জীবনবৃত্তান্ত জানা
ছিল। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে ডঃ হাওয়ার্ড এক জাতীয় অ্যানোফেলিস মশার জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। অ্যানোফেলিস মশকেরাই ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে বলে বিগত মহাযুদ্ধের সময় থেকে এদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলতে থাকে। ম্যালেরিয়ার মত ব্যাপক এবং মারাত্মক ব্যাধি বোধ হয় কমই
আছে। যদিও কুইনিন এবং তার অন্যান্য যৌগিক পদার্থসমূহ ম্যালেরিয়ার প্রতীকারার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তথাপি এটি সম্পূর্ণ অব্যর্থ নিরোধক নয়। রোগ-
বীজাণুবাহক অ্যানোফিলিস মশকের উৎপত্তি নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে ম্যালেরিয়া দমনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।
কেবল ম্যালেরিয়াই নয়- ক্রমশ দেখা গেল, অন্যান্য রোগও মশক কর্তৃক মনুষ্যদেহে পরিচালিত হয়ে থাকে। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে ডঃ রিড মশক সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায় যে, Aedes aegypti অথবা Aedes argeneus নামক একজাতীয় মশকের দংশনের ফলেই পীতজ্বর মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়। পীতজ্বরের উৎপত্তি পশ্চিম-আফ্রিকায়; কিন্তু পণ্যবাহী জাহাজাদির আশ্রয়ে রোগবীজাণু বাহক মশকেরা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে পরে জানা গেছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পীতজ্বরের বীজাণু বহনকারী প্রায় ১৩/১৪ রকমের মশকের অস্তিত্ব রয়েছে। এস্থলে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রোনাল্ড রসের আবিস্কারের প্রায় ১৯ বছর পূর্বে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে সার প্যাট্রিক ম্যান্সন দেখতে পেয়েছিলেন যে, Filaria bancrofti নামক কৃমিবৎ একপ্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোগবীজাণু জীবনের একাংশ মশকের উদরে অতিবাহিত করে থাকে। কিন্তু কি ভাবে এরা মশকের উদরে আশ্রয় গ্রহণ করে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তা জানতে পারা যায় না। ১৯০৩-৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জানতে পারা যায় যে, ব্যাপকভাবে সংক্রমণশীল ডেঙ্গু-জ্বরও Culex fatigins নামক মশকের সাহায্যে মনুষ্যদেহে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিস্তৃত গবেষণার ফলে পরে দেখা যায় যে, Aedes albopicus এবং Ades argenteus নামক মশকেরাই এই রোগের প্রকৃত বাহক।
মশক কর্তৃক এরূপ কয়েকটি সাংঘাতিক রোগ মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়, একথা প্রমাণিত হবার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মশকের জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবল উদ্যমে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলতে থাকে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২৪২টি বিভিন্ন জাতীয় মশকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে তিন হাজারের বেশী বিভিন্ন জাতীয় মশকের অস্তিত্বের খবর জানা গেছে। সকল জাতীয় মশকের বাচ্চাই জলে অবস্থান করে। তবে কোন কোন মশকের ডিম ফুটতে পাঁচ-সাত দিন মাত্র সময় লাগে আবার কারও কারও ডিম ফুটতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রবল স্রোত ব্যতীত পরিষ্কৃত, অপরিষ্কৃত, বদ্ধ বা মুক্ত, ছোট বড় যে-কোন জলাশয় বা জলাধারে মশকেরা তাদের ডিম পেড়ে রাখে। মশক বংশবিস্তারের অনুকূল অথবা প্রতিকূল স্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা নানাপ্রকার পরীক্ষা করতে থাকেন। এর ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। প্রথমে যাঁরা অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিলেন তাঁরা দেখলেন-কতকগুলি জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে অথচ তদনুরূপ অন্যান্য কতকগুলি জলাশয়ে একটিও মশক-শিশুর অস্তিত্ব নেই। তখন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, খাদ্যের প্রাচুর্য বা অভাববশতই এরূপ ঘটে থাকে। কেউ কেউ বললেন-ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ-পত্রাদি জলের উপরিভাগ আবৃত করে রাখলে সেখানে মশক-শিশুরা বাইরের বাতাস সংগ্রহ করতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে আবার এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, জলের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবৎ শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের আধিক্য হলে বাচ্চাগুলি তাতে জড়িয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য বিভিন্ন জাতীয় মাছ ও অন্যান্য জলজ পোকামাকড়েরা যে মশার বাচ্চা ধ্বংস করে থাকে এটাও অনেকে লক্ষ্য করেছিলেন।
যাই হোক, বিভিন্ন জাতীয় জলজ উদ্ভিদেরা যে মশার বাচ্চা ধ্বংসের কারণ হতে পারে এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অতি অল্পদিন পূর্বে। কতক- গুলি উদ্ভিদ যে মশা-মাছি উদরস্থ করে থাকে এ ঘটনা অবশ্য অনেক পূর্বেই জানা গিয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ডারুইন কীটপতঙ্গভুক উদ্ভিদের বিষয় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এদের শিকার ধরবার কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হতে পারেন নাই। ঐ সময়েই মিসেস্ ট্রীট কৃমি-কীটভোজী ইউট্রিকুলেরিয়া নামক জলজ উদ্ভিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য মৃত কীট দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু এর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে পারেন নাই। ১৯১১-২৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রোচার, হেগুনার প্রমুখ গবেষণাকারীদের বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে একথা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইউট্রিকুলেরিয়া জাতীয় জলজ-উদ্ভিদেরা কীট-পতঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ-কীড়াউ উদরস্থ করে দেহ পুষ্ট করে থাকে। ৭ ফুট লম্বা একটা ইউট্রিকুলেরিয়ার থলিগুলির মধ্যে হেগ্নার ১৫০,০০০-এর অধিক সংখ্যক কীড়া দেখতে পেয়ে- ছিলেন। এদের মধ্যে অসংখ্য মশার বাচ্চাও ছিল। এই হিসাবে মশক-নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে বিবেচনা করলে এই উদ্ভিদের কার্যকারিতার বিষয় সহজেই উপলব্ধি হবে। এতদ্ব্যতীত পানা-জাতীয় বিভিন্ন রকমের ভাসমান উদ্ভিদের সংখ্যাধিক্যের ফলে যে অনেক ক্ষেত্রে মশকের জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এটি অনেকে লক্ষ্য করেছে। অবশ্য কেউ কেউ এর বিপরীত দৃষ্টান্তের কথাও উল্লেখ করেছে।
জলের উপরে ভাসমান পানাজাতীয় উদ্ভিদ ছাড়াও সাধারণ লতাগুল্মের মত অসংখ্য রকমের জলনিমজ্জিত উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এরা জলের নীচে কর্দমাক্ত মাটিতে শিকড় চালিয়ে জলের প্রায় উপরিভাগ পর্যন্ত বেড়ে থাকে। এদের মধ্যে ‘কারাসি’ গণভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে অনেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মশক দমনে তাদের অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। কেউ কেউ আবার লক্ষ্য করেছেন যে, ‘কারা’ জাতীয় উদ্ভিদে আচ্ছন্ন এক জলাশয়ে মশার বাচ্চার চিহ্ন- মাত্র দেখা যায় না; অথচ অনুরূপ আর এক জলাশয়ে অসংখ্য বাচ্চা কিলবিল করছে। এরূপ পরস্পরবিরোধী ফলাফল দেখে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রোঃ ম্যাথেসন্ Chara vulgaris নামক জলজ-উদ্ভিদ নিয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। প্রকৃত কারণ কি-তা নির্ধারিত না হলেও তাঁর পরীক্ষার ফলে এটাই নিঃসন্দেহে রঝতে পারা যায় যে, এই জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ অধ্যুষিত জলাশয়ে মশক-শিশুরা মোটেই বৃদ্ধি পেতে পারে না।
মশক দমনে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ অবগত হবার পর কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশীয় অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স এবং অন্যান্য দুই- এক জাতীয় মশকের কীড়া এবং নাইটেলা, হাইড্রিলা, কারা, ভ্যালিনেরিয়া প্রভৃতি এদেশীয় জলজ-উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেছি। পরীক্ষার ফলে এ পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে এস্থলে তার মোটামুটি বিবরণ দিচ্ছি। প্রথমত উপরিউক্ত জলজ- উদ্ভিদগুলি কাচের জলাধারে উন্মুক্ত অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে রাখা হয়েছিল। পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার জলপূর্ণ আরও কতকগুলি উন্মুক্ত কাচের জলাধার পাশাপাশিই সজ্জিত ছিল। এদের একটিতেও জলজ-উদ্ভিদ রাখা হয় নাই। কয়েক দিন পরেই দেখা গেল জলজ-উদ্ভিদ-বিবর্জিত জলাধারগুলিতে কম- বেশী যথেষ্ট মশক-শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ একটি জলাধারেও মশক-শিশু দেখা যাচ্ছে না। দিন দুই পরে ভ্যালিনেরিয়ার জলাধারে গুটি তিনেক ক্ষুদ্রকায় মশার বাচ্চা দেখতে পেয়েছিলাম; কিন্তু তাও আবার দুই দিন পরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরীক্ষার ফলে দেখলাম-শেওলা অধ্যুষিত জল কিঞ্চিং ক্ষারধর্মী হয়েছে। তবে কি ক্ষারধর্মী জলে বাচ্চাগুলি বাঁচতে পারে না? ঐ জল অন্য পাত্রে ঢেলে রেখে দিলাম। পাঁচ-সাত দিন পরে দেখি তাতে কিছু কিছু মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে। উদ্ভিদ- বিবর্জিত এবং উদ্ভিদসমন্বিত উভয় প্রকার জলেই দু-চারটি করে ক্ষুদ্রকায় জল- পোকা ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা যেমন ছিল তেমনই আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ থেকে কম-বেশী অক্সিজেন-বুদ্বুদ নির্গত হত। হিঞ্চে, কলিম, জল-ঘাস প্রভৃতি অর্ধ নিমজ্জিত উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষার ফলে দেখলাম সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে। কাজেই উদ্ভিদ-দেহ নির্গত অক্সিজেনই মশক-ধ্বংসের প্রকৃত কারণ বলে মনে হল। যাই হোক, ফলাফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য জলজ-উদ্ভিদ পরিপূর্ণ জলাধারে
অন্য স্থানে থেকে মশক-শিশু এনে ছেড়ে দিলাম। দু-তিন দিনের মধ্যেই তারা প্রায় সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই রকম ফল দেখতে পেয়ে এবার সোজাসুজি অক্সিজেন প্রয়োগের ব্যবস্থা করলাম। অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে সূক্ষ্ম টিউব সহযোগে পোর্সেলিন ফিল্টারে মধ্য দিয়ে মশার বাচ্চা পরিপূর্ণ জলাধারের তলার দিক থেকে গ্যাস প্রয়োগ করতে লাগলাম। জলজ-উদ্ভিদ থেকে যেভাবে সূত্রাকারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুদ্বুদ উত্থিত হয় এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভাবেই অসংখ্য বুদ্বুদ উঠছিল। ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা গ্যাস প্রয়োগের সময় বাচ্চাগুলি যেন অস্বস্তিকর অবস্থায় কিলবিল করছিল। দু-তিন ঘণ্টা পর তাদিগকে আর বড় একটা উপরের দিকে উঠতে দেখা গেল না। সকলেই তখন জলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। দুদিন পর দেখলাম জলাধারে একটিও মশার বাচ্চার অস্তিত্ব নাই। গ্যাসের চাপ হ্রাস করে বুদ্বুদের সংখ্যা কমিয়ে দিলাম। তার ফলে দুদিন পরে দেখলাম, বাচ্চাগুলির সংখ্যা হ্রাস পেলেও সবগুলিই বিনষ্ট হয় নাই। বুদ্ধদের সংখ্যা কম রেখে গ্যাস প্রয়োগের সময় বাড়িয়ে দিলাম। দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল সমস্ত বাচ্চাই অদৃশ্য হয়েছে। অথচ যে-সকল জলাধারে গ্যাস প্রয়োগ করা হয় নাই তাদের বাচ্চাগুলি ক্রমে ক্রমে মশকে রূপান্তরিত হচ্ছিল। এই সকল ঘটনা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, খুব সম্ভব জলজ-উদ্ভিদ থেকে নির্গত অক্সিজেনই মশক শিশু বিনাশের কারণ ঘটিয়ে থাকে; কিন্তু কি ভাবে এটি কার্যকরী হয় তা বলা অধিকতর পরীক্ষাসাপেক্ষ।
আমাদের দেশে খাল, বিল ও অন্যান্য জলাশয়ে ইউট্রিকুলেরিয়া জাতীয় কীট- ভোজী জলজ-উদ্ভিদের অভাব নাই। মশার বাচ্চা পরিপূর্ণ জলাধারে এই গাছ- গুলিকে রেখে দেখেছি তারা অল্পদিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলিকে উদরস্থ করে ফেলে। অবশ্য ক্ষুদ্রকায় বাচ্চাগুলিই বেশীরভাগ এদের ফাঁদে পতিত হয়ে থাকে। তাছাড়া আমাদের দেশীয় গুড়ি-পানা, ইঁদুরকানী পানা প্রভৃতি যেসকল জলাশয়কে ঘন- সন্নিবিষ্টভাবে আবৃত করে রাখে তথায় মশার-বাচ্চা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হবে। পানার আবরণ ভেদ করে মশকেরা সাধারণত ডিম পাড়তে পারে না; আর ডিম পাড়লেও বাচ্চা বের হবার পর তারা জলের উপর থেকে বাতাস সংগ্রহ করতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে সকল জলাশয়ে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রং-বেরঙের আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের আধিক্যবশত পুরু সরের মত আস্তরণ পড়ে সে-সকল জলাশয়েও বোধহয় পূর্বোক্ত কারণেই মশক-শিশুর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। পানা অথবা আণুবীক্ষণিক ‘য়্যালগি’ জাতীয় উদ্ভিদের দ্বারা অংশবিশেষ আবৃত জলাশয়ের পক্ষে অবশ্য এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। মোটের উপর দেখা যায়, মশকেরা যেখানে সেখানে অনায়াসে জন্মগ্রহণ করতে পারলেও কেবলমাত্র মৎস্যাদি প্রাণীই নয়, বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদেরাও অহরহ প্রভূত পরিমাণে তাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রকৃতির রাজ্যে এইভাবেই সাম্য রক্ষিত হয়ে থাকে।