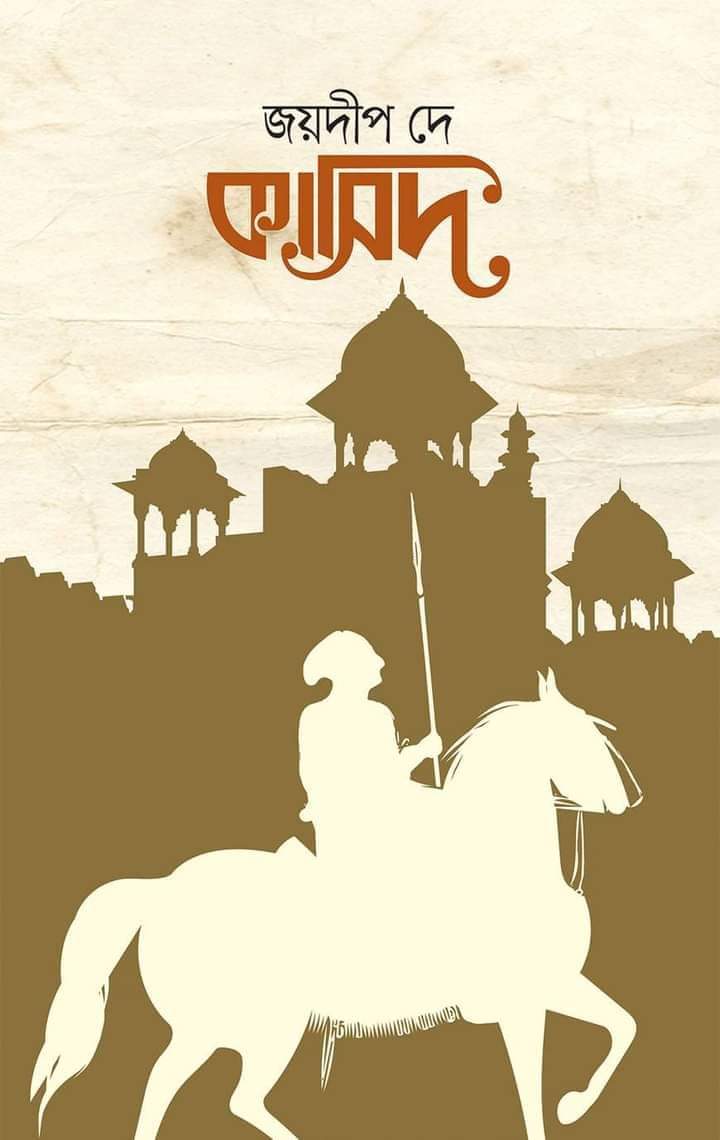#আশরাফ চৌধুরী
কাসিদ উপন্যাসটি নিছক ইতিহাস নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি নয়, এতে লেখক জয়দীপ দে নির্মোহভাবে একটি পরাক্রমশালী শাসকগোষ্ঠীর মহাপতনের সুলুকসন্ধান করেছেন। বংশানুক্রমিক শাসনের চুড়ান্ত পরিণতিকে পাপতাপের নিক্তিতে মাপবার চেষ্টাও লেখক এতে করেননি। জনগনের সাথে দুরত্ব কিভাবে রাজা-বাদশা-নবাবদের ঢাল-তলোয়ারবিহীন নিধিরাম সর্দারে পরিণত করে তার ঝরঝরে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কাসিদ এ। উপন্যাসে লেখক টনটনে আবেগের পসরা সাজাতে যাননি বা ধান বানতে শিবের গীতও গাননি। কাসিদ মানে বার্তাবাহক। সত্যিকার অর্থেই ইতিহাস আশ্রয়ী এই উপন্যাসটি ভারতীয় উপমহাদেশের আমজনতার রাজনৈতিক মানসের বার্তাই যেন বহন করছে।
ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস লেখার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো পাঠককে Historical Chronology এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কাসিদে পাঠক প্রস্তুত করার এই কাজটি দক্ষতার সাথে করে লেখক পাঠককেই চমকে দিয়েছেন। বলা যায় ঘটনার পূর্বাপর অন্তর্নিহিত বাঁকগুলো জানা পাঠকের যে দায়িত্ব তা তিনি নিজের কাঁধেই যেন তুলে নিয়েছেন। এর ফলে পাঠক পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে ফেলেন না বা হাঁপিয়ে ওঠেন না। লেখক উপন্যাসের শুরুতেই ‘সন্ধ্যারাগ’ এ পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন দিল্লিশ্বর মুহাম্মদ শাহের সাথে। এ যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অসীম জলরাশশির ঝর্ণাধারা হয়ে জলপ্রপাতে মিশে যাওয়ার মহা আয়োজন। কাসিদ পড়ার পর সিরাজের ধ্বসে পড়া বা মুঘল সম্রাজ্যের পতন অনিবার্য ছিল নাকি শাসকদেরর কর্মকাণ্ডের পরিণতি এই দ্বিধা জাগাও স্বাভাবিক। তবে ফিকশনে লেখকের এই অধিকার থাকেই। জয়দীপ দে এক্ষেত্রে নিপুণভাবে পাঠককেও উপন্যাসের স্টেক হোল্ডার বানিয়েছেন।
মনসবদারদের বুজরুকি হিসেবের ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রায় অভ্যস্ত নবাব কিভাবে তার অর্ধ লক্ষ বাহিনী নিয়ে পলাশীর আম্রকাননে মাত্র তিন হাজার ভিনদেশী সৈন্যের ইংরেজদের কাছে পর্যদুস্ত হলেন, তা শুধু আবেগ দিয়ে বিচার করা যে সমীচীন নয়, সেটা লেখক কাসিদ এর পাতায় পাতায় স্পষ্ট করেছেন। প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার, সুদূরপ্রসারি সমরনীতি, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, সুনির্দিষ্ট পররাষ্ট্রনীতি, সময়োচিত সাহসিকতা, তুখোড় কূটনীতি ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ কিভাবে একটি ভাসমান জাতিকে সুবিশাল এক সম্রাজ্যের অধিপতি বানিয়ে দেয় তা লেখক সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন কাসিদ’এ। অপরদিকে লোভ, দ্বন্দ্ব, খামখেয়ালিপনা, মিথ্যা অহংকার, ভোগবিলাস, ষড়যন্ত্র, দুর্বল অর্থব্যবস্থাপনা, বিশ্বাসঘাতকতা, শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা আর অপরিণামদর্শিতা মহাপরাক্রমশালী শাসকদের কিভাবে রাস্তায় টেনে নামায় তা জানতে হলে কাসিদ পড়তে হবে।
লুমিংটন, ডুপ্লে, বিষ্ণু প্রসাদ, মোহনলাল, রাইচরণ, রহিম, চম্পা ও রহস্যময় গোবিন্দসহ ছোটছোট চরিত্রগুলোর মাধ্যমে কাসিদ লেখক এঁকেছেন বাংলা-বিহার-উড়িষার শেষ স্বাধীন নবাবের পতনের লেখচিত্র। এই চরিত্রগুলো যেন একেকটা কাসিদ। যেমন উপন্যাসের এক জায়গায় লুমিংটন ভাবছেন-‘ব্রিটিশরা মাত্র ২৫ হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে ভারতে এসেছিল। এখানে তাদের তেমন কোন পণ্যই বিক্রি হতো না। একসময় পাততাড়ি গুটিয়ে ইংল্যান্ড চলে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। অথচ ভারতে এমন ব্যবসায়ী আছে যাদের হাতে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু এদের সাহস নেই। নেই উদ্যম। বড় কথা রাজশক্তির সমর্থন নেই ব্যবসা বিকাশে।’
৩২ পৃষ্টায় চম্পা বাইজি নবাব আলিবর্দি সম্পর্কে বলছে- ‘তিনি জানেন চাতুরীর জয়, পরাজয়ের চেয়েও খারাপ। তিনি পাটনা থেকে রওনা দিয়েছিলেন ভোজপুরের জমিদার দমনের কথা বলে। বাংলার সীমান্তের কাছে এসেই বোল পাল্টে ফেললেন। এত বীরের কাজ হতে পারে না। আশ্রয়দাতার পুত্রকে যে হত্যা করতে পারে, তার পক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে জঘণ্য কর্মটি করা সম্ভব’।
১১৭ পৃষ্ঠায় ফস্টার নবাব আলিবর্দির ইংরেজদের কাছে আরবি ঘোড়া চাওয়া নিয়ে ঠাট্টা শেষে আসল কথা পাড়লেন -‘শোনো লুমিংটন, এই যুগ বিত্তের নয় বিদ্যার। এরা বিদ্যাবিমুখ। প্রবৃত্তি নির্ভর। এরা বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না’।
আরেক স্থানে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে নিয়ে রায়চরণের আক্ষেপ -‘ঠাকুর এদের মাজায় জোর দিয়েছে। কে বলবে হপ্তাখানেক আগে এই নবাব ভিনদেশ থেকে আসা হাতেগোনা কটা বণিকের সঙ্গে লড়াই করে হেরে নাক খত দিয়ে এসেছে। কোন বিকার আছে? কোনো লজ্জাবোধ? এমন ভোগপ্রবণ নবাব এই বিশাল রাজ্যটাকে রক্ষা করবে কী করে?’
মোঘল সম্রাজ্য পতনের অন্যতম প্রধান কারন তাদের শক্তিশালী নৌবাহিনী না থাকা। এই বিষয়টিকে লেখক তুলে ধরেছেন তার প্রাজ্ঞ লিখনশৈলীতে। ৯৫ ও ৯৬ পৃষ্ঠায় লেখক লিখছেন -‘ বলা যেতে পারে সুরাটের আব্দুল গফুরের কথা। তিনি সুরাটের বিরাট ব্যবসায়ি ছিলেন। তার অন্তত বিশখানা বিশাল বিশাল জাহাজ ছিল। কিন্তু এসব জাহাজ নিয়ে দূরযাত্রা করতেই পারত না। ইউরোপীয় দস্যুরা সব লুটপাট করে নিত। ১৭০১ সালে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বাদশার প্রতিনিধি ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বিপুল পরিমাণ অর্থদণ্ড করে। ইউরোপীয়রা তখন উল্টো হুমকি দেয়, আচ্ছা দেখব, ভারত থেকে লোকজন কীভাবে হজ্বে যায়। মুঘলদের গভীর সমুদ্রে কোনো নৌশক্তি ছিল না। ভয়ে বাদশা পিছু হটেন। শেষমেশ গফুর জাহাজ ব্যবসাই ছেড়ে দেন।’
কাসিদ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় The grand fall of an Empire এর স্বরূপ। এই পাঠকদের অনেকের কাছে বিশ শতকের নাটক-সিনেমা-যাত্রাপালায় ‘সিরাজুদ্দৌলার ইতিহাস সিরাজুদ্দৌলা থেকেই শুরুর হাস্যকর প্রচেষ্টা মোটামুটি বিরক্তিতে ঠেকেছে। আমাদের পাঠকদের বলা হয় তারা সিরিয়াস পাঠক নন। কিন্তু যে বিষয়টা বলা হয় না তা হলো- পাঠের মত লেখা হলে পাঠকের অভাব হয় না। এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা বলা উচিৎ মনে করছি- পাঠক তৈরির দায় কেবল কবি বা লেখকের উপরই বর্তায় না। প্রকাশক, সমঝদার, প্রতিষ্ঠিত লেখক বা কবিদের ইতিবাচক অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশসহ অন্যান্য অনুষঙ্গও এতে ভূমিকা রাখে। তবে, ইতিহাস নির্ভর উপন্যাসের পাঠক তৈরিতে অদূরভবিষ্যতে কাসিদ ভূমিকা রাখবে এমন প্রত্যাশা করা যেতেই পারে।
আমরা জানতে পারি কাশিমবাজার কুটিই সিরাজুদ্দৌলার পতন নকশার একমাত্র আঁতুড়ঘর নয়। ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল চেহেল সেতুন, জাফরগঞ্জ প্রাসাদ বা জগতশেট মহাতপ রায়ের বাড়ি। কিংবা মেহেরুন্নেসা, যিনি ঘসেটি বেগম নামেই সমধিক পরিচিত। মীর জাফরের ক্ষোভ নিতান্ত অন্যায্য নয়। পাঠক জানতে পারে জগৎশেঠ মহাতপ রায়কে খামখেয়ালি অবিমৃষ্য তরুণ নবাব অপমান না করলে হয়তো তার পরিনতি এমন ট্র্যাজিক নাও হতে পারতো। এবং ঘসেটি বেগমের প্রতি নবাব আলিবর্দি খানের দুর্বলতার কারণ মারাটা আক্রমণে পর্যুদস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণে সহায়তা বা নবাবের বিহার অভিযানের সময় টাকার টান পরলে এই ঘসেটি বেগমের এগিয়ে আসা। কাসিদ জানাচ্ছে মীর বক্সি মীর জাফর আলি খান ও তার বোনের সতিনের ছেলে খাদেম হোসেন খানের সমকামিতার গল্প।
কাসিদ উপন্যাসের লেখক জয়দীপ দে গল্প বলার ছলে অনেকগুলো তথ্য জ্ঞান অন্বেষক পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন যেমন- ‘আর্মাড’ শব্দটি থেকে ‘হার্মাদ’ শব্দটি এসেছে বা অশ্বারোহী মারাঠা যোদ্ধাদের ‘বারগি’ বলা হয় ”যা পরবর্তীতে মুখেমুখে ফিরে ‘বর্গি’ হয়ে যায়”। আছে ভাস্কো দা গামা কালী দেবীর পূজাকে মাদার মেরিকে পূজা মনে করে ভারতীয়দের খ্রিস্টান হিসেবে রিপোর্ট করার মত চমকপ্রদ তথ্য। আরো আছে নিজেদের চরম দুঃসময়ে কিভাবে একজন স্বজাতি প্রেমিক ইংরেজ ডাক্তার গেব্রিয়েল বৌটন সম্রাট শাহজাহানের অগ্নিদগ্ধ কন্যা জাহানারার চিকিৎসার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি আদায় করেছিলেন সেই তথ্য। আমরা জানতে পারি- ‘হিরাঝিল প্রাসাদ বললেও সিরাজের প্রাসাদের নাম মূলত মনসুরগদি’। সিরাজুদ্দৌলা বাংলার নবাব কিন্তু তিনি বাংলা বুঝতেন না। কাসিদ জানাচ্ছে- গঙ্গা থেকে একটা শাখা দক্ষিণে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সাগরের দিকে। লম্বায় আড়াইশ কিলোমিটারের মত হবে। উজানে একে লোকে ভাগীরথী বলে। ভাটির মানুষ বলে হুগলি।’ আমরা আরো জানতে পারি কলকাতা নামক শহরের গোড়াপত্তনের ইতিহাস।
চরম বেদনায় পাঠক লক্ষ করেন তথাকথিত সিলেক্ট কমিটি কীভাবে বাংলা বিহার উড়িষার ভাগ্য আড়াই কোটি টাকায় নির্ধারণ করে। আর কিভাবে মীর জাফর, রায় দূর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেট মহাতপ রায়, ওয়াটসন, কর্নেল ক্লাইভ, ড্রেক, ওয়াটস, মেজর কিলপ্যাট্রিকরা বিচারের এই গোলামীর দাসখতে সম্মতি দেয়।
সিরাজের বিয়োগান্তক পতনের পর বাংলার সম্পদ কীভাবে ইংরেজরা লুট করে তার হৃদয়বিদারক বর্ণনা লেখক দিয়েছেন ২৫৬ পৃষ্ঠায়- ‘…. টাকা ভাগযোগের পর সাতশত সিন্দুকে ভরে তা একশত নৌকায় তোলা হয়।…..
কাসিদ উপন্যাসে লেখক জয়দীপ দে বাংলার নবাবদের নিয়ে গড়ে উঠা নানা লোকগাঁথা, ছড়া, চারণ কবিতা, শ্লোক-স্তবকগুলো নিবিড় যত্নে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন দারুণ মুন্সিয়ানায়।
কৌতূহলোদ্দীপক পাঠকদের জন্য সবচেয়ে যেটা চমকপ্রদ তা হলো কাসিদ এর প্রতিটি অধ্যায়ের সার্থক নামকরণ। সন্ধারাগ, ভাগীরথী থেকে হুগলি, শঠ ও শেঠ, অস্থির চতুরঙ্গ, ঈষাণ কোণে কালো মেঘ, চক্রান্তের চক্র, বাজে দুন্দুভি, টাকা উড়ে বাতাসে, সম্মুখ সমরে, নিভে গেল দীপসহ বিভিন্ন অধ্যায়ের অসাধারণ নাম যোগ। পরিশিষ্টে ঘটনাপ্রবাহের সংযোজন, ঝকঝকে ছাপা প্রয়োজনীয় ছবি-ম্যাপ ও রেফারেন্স বইয়ের তালিকাসহ কাসিদ যেন ইতিহাসপ্রিয় বুভুক্ষু পাঠকের ক্ষুধা নিবারণে এক অনন্য ব্যঞ্জন ।
ইতিহাস নির্ভর একপেশে ফিকশন পড়ার একঘেয়েমি থেকে পাঠককে মুক্তি দেওয়ার জন্য কাসিদ লেখককে ধন্যবাদ না জানালে অবিচার হবে। জয়দীপ দে কে পাঠকমহল ভবিষ্যতে কাসিদ এর লেখক হিসেবে চিনবে নাকি তার তূণের আরো আরো নতুন তীর পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করবে সে প্রশ্ন ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক। তবে তিনি পাঠকের মধ্যে যে পিপাসাবোধ জাগিয়েছেন তা মেটানোর দায়িত্বতো তারই। আপাতত আমরা না হয় কাসিদেই বুঁদ হয়ে থাকি।