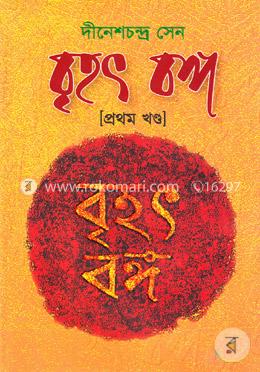চট্টগ্রাম, ৮ নভেম্বর, ২০২৩:
পৌরাণিক যুগের কল্পনার কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া যে সত্যের আলোটুকু আসিয়াছে তাহাতে বৃহৎ বঙ্গের মানচিত্রকে খুব উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছে। অপিচ আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ-সমাশ্রিত যে আর্য্যদর্শনের অভ্যূতয় হইয়াছিল তাহাতে ব্রাহ্মণকে দেবতা হইতেও উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছিল। এই গৌরব ও পূজার প্রধান পতাকাবাহী ও পুরোহিত ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ।
পূর্ব্বকালের অর্থাৎ বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণ ছিলেন অন্যরূপ। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-রক্তের উপর ততটা জোর দেন নাই। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইত এবং প্রধানতঃ বৃত্তিই জাতি-নির্দ্দেশক ছিল। যে কোন জাতির লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। এমন কি কোন কোন মহর্ষি গণিকাজাত ছিলেন। সত্যকাম ও নারদের মাতার স্থান এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে।
কিন্তু মহাভারতের যুগের পর হইতে ব্রাহ্মণগণ যে ক্ষমতা পাইলেন, তাহা তাঁহাদিগের অপ্রতিদ্বন্দ্বি শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ভাবে প্রতিপন্ন করিল। বঙ্গদেশের রাজারা, এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষের রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন; অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্রাটগণও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে ব্রাহ্মণকে স্বর্গমর্ত্যের সর্ব্বোচ্চস্থানে যেভাবে আসীন করা হইয়াছে, পূৰ্ব্ব-ভারতবাসিগণ প্রথমতঃ তাহা স্বীকার করেন নাই। মহাভারতে যজ্ঞাদির যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও ফলশ্রুতি আছে এবং বিশেষ করিয়া অনুশাসন-পৰ্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপের যে সকল উপগল্প লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রভাব প্রথমতঃ এদেশ স্বীকার করে নাই।
মহাভারতকার লিখিয়াছেন-ব্রাহ্মণের সেবা করিলে ইহলোকে ও পরলোকে এমন কোন অভীপ্সিত সামগ্রী নাই, যাহা মানুষে না পাইতে পারে। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম জোর দিয়া বলিল ‘কাহাকেও কিছু দিবার ক্ষমতা অপরের নাই। কর্মই লোকের অদৃষ্ট নির্ম্মাণ করে এবং কৰ্ম্মই সৰ্ব্বফলগ্রন্থ’।
মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাবাদ আছে তাহার কিছু নমুনা আমরা নিয়ে দিতেছি।
ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, ‘ফলতঃ ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যার কিছুই নাই, আমি ব্রাহ্মণগণের দাস। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতিই পরমধৰ্ম্ম, পতিই দেবতা ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কূলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধৰ্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও পরমগতি। অরণ্য মধ্যে অগ্নিশিখা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে সমুদার ভষ্মসাৎ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই। বাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য। উহারা দেবতাকে অপদেবতা ও অপদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। মুষ্টিদ্বারা বায়ুগ্রহণ ও হস্তদ্বারা চন্দ্রস্পর্শ ও পৃথিবীধারণ করা যেরূপ, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন।
সাতাইশ নক্ষত্রের কোন কোনটিতে ব্রাহ্মণকে কি কি খাওয়াইলে বা দিলে স্বর্গলাভ হয় তাহার একটা দীর্ঘ তালিকা আছে, যথা- কৃত্তিকায় ঘৃত, পায়েস; রোহিণী নক্ষত্রে মৃগমাংস; মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎস ধেনুদান, আদ্রায় তিল মিশ্রিত কেশর; পুনর্বসুতে পিষ্টক ও অন্ন; পুষ্যায় সুবর্ণদান; অশ্লেষায় রজত ও বৃষদান; মগায় তিল সমৃদ্ধ সরাব ইত্যাদি।
ফলশ্রুতিতে দাতাদিগকে নানারূপ লোভ দেখান হইয়াছে, যথা “চিত্রা নক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অস্পরাদের সঙ্গে নন্দনকাননে বিহার করিতে পারা যায়। এই অগণিত দানদ্রব্যের মধ্যে রাজকীয় বিলাস সামগ্রীর অভাব নাই, যথা—হাতি, রথ, কম্বল, শ্বেতবর্ণমাল, মেষমাংস এবং অগুরু চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। যে যে বিখ্যাত পুরুষেরা ব্রাহ্মণদিগের এবংবিধ দান করিয়া স্বর্গের সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের নামের এক দীর্ঘ তালিকা আছে। আমরা সহিষ্ণু পাঠকবর্গের ঘাড়ে সেই মুষল চাপাইব না।
এমন কি স্বীয় পরিণীতা ভার্য্যাকে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কোন রাজা প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপের আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব—“ব্রাহ্মণদিগের শাপ প্রভাবেই সাগবের জল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে, উহাদের কোপানল দণ্ডকারণ্যে এখনও প্রশমিত হয় নাই। উহারা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ, প্রমাণের প্রমাণ। উহাদিগের মধ্য কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেই পূজার যোগ্য। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য, তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন বা মূর্খ হউন-তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা বিধেয়।
অগ্নি সংস্কৃতই হউন বা অসংস্কৃতই হউন, তাঁহার দেবত্ব কিছুতেই লুপ্ত হয় না। যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হন না, প্রত্যুত গৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জানিয়া সমাদর করিবে। “ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্-সমূহ ব্রাহ্মণ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন ।
.
পরশুরামের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বড় কি, ক্ষত্রিয় বড় সমাজে একবার এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। পালি “অম্বঠঠসুত্ত” নামক পুস্তকে দেখা যায়, বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়দিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বেই একবিংশবার যুদ্ধ করিয়া পরশুরাম ক্ষত্রিয়কূল নির্মূল করিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যাৰ্জ্জুনও পরশুরাম কর্তৃক নিহত হওয়ার পর মহানন্দ প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে নিরস্ত হইয়া অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অনেকে কিরূপ দীনভাবে বাহ্মণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে।
ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব ও ব্রাহ্মণ্য-জাতিভেদের কড়াকড়ি ভারতে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এই ব্রাহ্মণ-শিক্ষাদীক্ষার ভিত্তিভূমি মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বের দশম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। “হীন জাতিকে উপদেশ দেওয়া কখনই কৰ্ত্তব্য নহে।” “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন কখনই ভোজন করিবেন না”। বৈশ্যের অন্ন-সম্বন্ধেও কতকগুলি নিষেধ-বিধি আছে। এ দিকে যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসক, অস্ত্রজীবী, পুরাধ্যক্ষ, দেবল ও দৈবজ্ঞ তাঁহাদিগকেও যুদ্ধের পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে। যাহারা বেতন লইয়া অধ্যাপনা করেন——সেইরূপ বাহ্মণেরও অন্ন নিষিদ্ধ হইয়াছে।
প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে মনুস্মৃতি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাহ্মণ-রাজ পুষ্যমিত্রের সময়ে ফিরিয়া লেখা হইয়াছিল, তখন তাহাতে উহার বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল; পুষ্যমিত্র মৌর্য্যরাজের সেনাপতি ছিলেন, শেষে স্বভৃত্যকে হত্যা করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করেন। আশ্চর্য্যের কথা বিষয়-বিরাগে ব্রাহ্মণ যে পার্থিব ভোগ-বিলাসের যোগ্য পাত্র, তাহা এই মানব-স্তুতির
নব সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে।
ব্রাহ্মণ সেনাপতি হইতে পারেন, রাজা হইতে পারেন, ইত্যাদি ব্যবস্থা স্পষ্টরূপে সংশোধিত মনু-স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ রাজার কার্য সমর্থন করিতেছে, “সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব । সৰ্ব্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্র বিদর্হতি।” সমস্ত পৃথিবীর অধিকার ন্যায্যত ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, এ কথাও মানব-ধৰ্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়।
সুম্ধবংশের পূর্ব্বে রাহ্মণের অপরাধের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পরবর্তী স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণের দণ্ড অতিলঘু করিয়া দেন। শূদ্রদের উপর শাস্তির ব্যবস্থা এই সময়ে কঠোরতম হইয়া দাঁড়ায়। এতদ্বারা সুম্ধ বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের স্বজাতিকে বাড়াইবার প্রবল চেষ্টা ও মৌর্যদিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ সূচিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে পরবর্তী কালে যে সকল অনুশাসন শাস্ত্রীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও সূত্র মহাভারতেই পাই—”পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরমা গতি। অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য ও বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না তিনি পতিব্রতা ধর্ম্মের ফল লাভ করিয়া থাকেন”। এই উক্তির সঙ্গে নারদপঞ্চচূড়া-সংবাদের নানারূপ জঘণ্য কথা মিলাইয়া পড়িলে স্ত্রীলোকদিগের উপর শাস্ত্রীয় কঠোর বিধির কারণ উপলব্ধ হইতে পারে।
মহাভারতে এই যে বাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা আছে, তাহা আর দ্বিসহস্র বৎসর হিন্দু
জনসাধারণের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে এরূপ অদ্ভূত ও অচলা ব্রাহ্মণভক্তির লীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম সমস্ত জাতির অন্ত দীক্ষার দ্বার খুলিয়া দিলেন– যজ্ঞধর্ম্মের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন, তাহারও দ্বিসহস্র বৎসর পরে চৈতন্য ‘চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণ’ সাম্যের এই মহাবাণী প্রচার করিলেন।
কিন্তু বৌদ্ধ যুগ হইতে এই সকল ধর্ম গুরুগণের সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী উপেক্ষিত অস্বীকৃত হইলেও তাহাদের জন্য একটা শ্রদ্ধার আসন “সর্বত্রই নির্দিষ্ট ছিল। অধুনা রাহ্মধর্ম্ম সেটুকুও অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি কি অমোঘ বিশ্বাস কি অচলা ভক্তি হিন্দুসমাজের অস্থিপঞ্জরে প্রবেশ করিয়া আছে। এখনও জনসাধারণের মধ্যে সে বিশ্বাস কতক পরিমাণে অনড় হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোক কাহারও মুখ দেখিতে পারিবে না, মহাভারতীয় এই নীতির খুব বাড়াবাড়ি অভিনয় হইয়াছে।
স্বর্গীয়া রাসমণির জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে, তিনি স্বামীর ঘোড়াটা দেখিয়া লজ্জায় একহাত ঘোমটা টানিয়া দিয়া তথা হইতে পলাইয়া গিয়াছিলেন। ইহা গল্প-গুজব নহে, সত্যকার ঘটনা, রাসমণি স্বয়ং লিখিয়াছেন। অবশ্য গাছ দেখিয়া লজ্জা পাওয়ার উদাহরণ এখনও পাই নাই। প্রচলিত “অসূৰ্য্যস্পর্শা” কথাটাতে সূর্যের দৃষ্টি হইতেও মেয়েদের আত্মরক্ষার ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি।
জাতিভেদ এবং অন্নভোজনের যে কড়াকড়ি এদেশে হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, — সমস্ত ধর্মতত্ত্ব হাঁড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নৈষ্ঠিক হিন্দু রন্ধনশালায় সতর্ক পাহারা দেওয়াই পরম ধৰ্ম্ম মনে করিয়া থাকেন। মহাভারতকার বলিয়াছেন, শূদ্রান্ন, শিল্পী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিতসদৃশ”। উত্তরকালে বৌদ্ধ ধৰ্ম্মকে নিরস্ত করিয়া যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম শির উত্তোলন করিয়াছিল, তাহা এই সকল উপদেশ মূলধনের ন্যায় বিশেষ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল।
বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি হিন্দুদর্শনে পুর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, বাহ্যিক অনুষ্ঠান অনেক স্থলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মহাভারত ব্রাহ্মণদিগের মাহাত্ম্যের অতিশয়োক্তি ও যজ্ঞের সমর্থন করিয়াও ‘জীবে দয়া’ নীতির কথা ভুলিয়া যান নাই। কিন্তু বৈদিক যুগ হইতে এ পর্যন্ত কোন কালেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি এ দেশে একেবারে নির্বাপিত হয় নাই। যখন উহা নির্বানোম্মুখ হইয়াছিল, তখন সেন রাজাদের মাতৃকূলের কোন আদি পুরুষ তিনি সুর বংশীয় হউন বা অপর কোন বংশীয়ই হউন–সুদূর পশ্চিম হইতে নব ব্ৰাহ্মণ্যদীক্ষিত সাগ্নিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারগ ব্রাহ্মণদিগকে এখানে আনিয়া তাঁহাদিগকে সপ্তম শতাব্দীতে এ দেশের ধর্ম্মগুরু ও সমাজগুরুরূপে অধিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। সেই কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া আমরা এখন পর্যন্ত তাঁহাদের বিধান শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি।
কিন্তু তাঁহাদের অধিকারে যুগে যুগে অনেক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। এই বিদ্রোহীদলের সর্ব্বজনস্বীকৃত অধিনায়ক ছিলেন সপার্শ্বদ চৈতন্যদেব।
তন্ত্ররত্নাকরে লিখিত আছে, ত্রিপুরাসুর হত হইলে বটুকভৈরব গণদেবকে জিজ্ঞাসা করেন ত্রিপুর নিহত হওয়ার পর তাহার সত্তা জগৎ হইতে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল,—না কোন না, কোন প্রকারে বিদ্যমান ছিল। গণদেব উত্তর করিলেন, ত্রিপুরাসুর হত হইলে তাঁহার রূপ তিনভাবে জগতে দেখা দিয়াছিল- সেই মহাতেজা অসুরের প্রধান অংশ শচীগর্ভে চৈতন্যরূপে প্রকট হইল, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতরূপে আবির্ভূত ইয়াছিল। ইহারা সম্মুখযুদ্ধে শিব-শক্তির বিরুদ্ধতা করিতে অসমর্থ হইয়া মানুষকে হীনবল করিবার জন্য নারীভাবের উপাসনা শিক্ষা দান করিল।
নব-ব্রাহ্মণ্য-ধৰ্ম্ম যাহা আপৎকালের ধর্ম্মের ন্যায় সময়ের প্রয়োজন বুঝিয়া সমুদ্রযাত্রা নিষেধ, স্ত্রীলোকের প্রতি অবিচার এবং প্রবহমান স্বাভাবিক ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়া জাতিভেদ ও আহার-সংযমের গল্প শত শত নিষেধবিধি দ্বারা সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে কৃত্রিমতা আনয়ন করিয়াছিল—তৎবিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতি পুনঃ পুনঃ সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক সনাতন ধর্মের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছে।
চৈতন্যদেব প্রাচীন সমাজের প্রধান এবং প্রথম বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ আধুনিক সময়ে রামমোহন রায় ঘোষণা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি গান্ধী-প্রবর্তিত নীতিতে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিত বোধ হয় একেবারে ধসিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী কোন কালেই স্বাধীনতার ডাক অগ্রাহ্য করে নাই। চিন্তাব সঙ্কীর্ণতা, কোন ধর্ম্মমতের অস্বাভাবিক অনুজ্ঞা তাহারা বেশি দিন সহ্য করে নাই। জরাসন্ধ, নরক, মুর প্রভৃতির সময় হইতে বৃহৎ বঙ্গ চির দিন স্বাধীনতার যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে এই যুদ্ধলীলা বিশেষভাবে সংঘটিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শেষে একটি কথা আমাদের বক্তব্য।
মহাভারতেই আমরা নব ব্রাহ্মণ্যের সূচনার লক্ষণ সকল দিকে দেখিতেছি, –রন্ধনশালাকে দর্শন-স্পর্শনের অতীত অতি পবিত্র মন্দিরে পরিণত করা, জাতিভেদের অচ্ছেদ্য প্রাচীর উত্তোলন করা, স্ত্রীলোককে কোঁটায় পুরিয়া বাখা, সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণদিগকে অন্য সৰ্ব্বজাতি অনধিগম্য ঊর্দ্ধ-লোকে স্থান দিয়া তাহাদিগকে দ্যুলোক-ভূলোকের একাধিপত্য প্রদান করা—এ সমস্তই সূত্রাকারে মহাভারতে দেখিতে পাই।
#লেখাটি কবি ও ইতিহাসবিদ ড. দীনেশ চন্দ্র সেন-এর গ্রন্থ ‘বৃহৎ বঙ্গ’ প্রথম খণ্ডের ‘ সপ্তম পরিচ্ছেদের ‘নব ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম’ এর সংক্ষেপিত অংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।
লেখক পরিচিতি : ড. দীনেশ চন্দ্র সেন(৩ নভেম্বর,১৮৬৬- ২০ নভেম্বর,১৯৩৯) শিক্ষাবিদ, গবেষক, লোক-সাহিত্যবিশারদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো এবং এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন।
দীনেশচন্দ্র সেন মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন মানিকগঞ্জ আদালতের উকিল ছিলেন। মাতা রূপলতা দেবী। হীরালাল সেন তার খুড়তুতো ভাই। কবি ও সাংবাদিক সমর সেন তার পৌত্র।